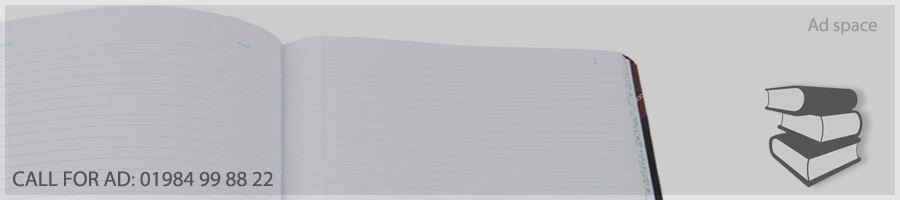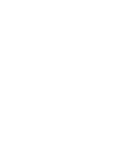মডার্নিজম ॥
ইসলামী শরীয়ার আধুনিকীকরণের নামে বিকৃতিসাধন : ইতিহাস, প্রেক্ষাপট ও মৌলিক বিচ্যুতি
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
প্রাচ্যবিদদের গবেষণার মৌলিক ত্রুটি
ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যবিদরা হল সেই দুর্ভাগা দল, যারা বারবার ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমুদ্রে ডুব দিয়েও কোনো বিষয়ের সঠিক, স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান আহরণ করতে পারে না। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ইসলাম সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তারা অনেক পরিশ্রম করেন। তবে পূর্ণ সততার সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, যৌক্তিক মানদণ্ডে তাদের দাবিগুলোর জ্ঞানগত বা বুদ্ধিবৃত্তিক ওজন নেই। তারা কোনো বিষয়ে লিখলে সেই বিষয়ের বহু মৌলিক দিক সম্পর্কে বেখবর থাকেন। দুটি উদাহরণ দেখুন–
ক. প্রাচ্যবিদ ডেভিড দে সান্তিয়ানার(১) একটি প্রবন্ধ The Legacy of Islam -এ প্রকাশিত হয়েছিল; এর উর্দু অনুবাদ করাচির چراغ راہ পত্রিকার اسلامى قانون نمبر (‘ইসলামী আইন সংখ্যা’)-এ ছেপেছিল, শিরোনাম ছিল–
اسلامى قانون اور نظام معاشرت
(‘ইসলামী আইন ও সমাজব্যবস্থা’)। পরিশ্রম করে প্রবন্ধটি লিখলেও শুরুতেই (তাওহীদসহ ইসলামের কিছু মৌলিক আকীদার কথা লিখে) বলেন–
All these ideas are already set forth in the oldest historical document of islam, the charter promulgated at Medina in the year one of the Hijrah.
‘এইসব আইডিয়া (আকীদা) ইসলামের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নথি মদীনা সনদে বিবৃত হয়েছে, যা হিজরী প্রথম বর্ষে জারি করা হয়েছিল।’ (Thomas Arnold and Alfred Guillaume, eds., The Legacy of Islam, First edition, Oxford University Press, 1931, p. 285)
জানা কথা, হিজরতের তেরো বছর আগে মক্কায় কুরআন অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছিল, (তখনই কুরআনে ইসলামের মৌলিক সব আকীদা বিবৃত হয়েছে। তাই ‘এই আকীদাসমূহের উৎস মদীনা সনদ’– এই কথা বাস্তবতা সমর্থিত নয়। বরং একদিক থেকে এই কথা ইসলামের মৌলিক উৎস সম্পর্কে লেখকের জ্ঞানগত অজ্ঞতার স্পষ্ট দলীল) (২)
খ. প্রফেসর স্মিথ, যাঁর কথা আগে বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছি, তাঁর প্রবন্ধের (উর্দু অনুবাদ اسلام ميں قانون اور اجتهاد ‘ইসলামে আইন ও ইজতিহাদ’ নামে ছাপা হয়েছে) এক স্থানে দাবি করেছেন–
‘হাদীসে বলা হয়েছে–
تتغير الأحكام بتغير الزمان.
‘সময়ের পরিবর্তনে আইন-কানুন পরিবর্তন হয়’ (পৃ. ৫)।
দেখুন, ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমামগণের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদরা অভিযোগ তুলেছে যে, তাঁরা হাদীস শরীফকে যথাযথ সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে অনেক ভুল কথা প্রচার করেছেন, নাউযুবিল্লাহ! অথচ স্মিথের কাণ্ড দেখুন, ফকীহদের একটি কথাকে কীভাবে হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছেন!
তো প্রাচ্যবিদরা ‘ব্যাপক’ পড়াশোনা ও ‘কঠোর’ পরিশ্রম সত্ত্বেও এমন কাঁচা ভুল করে বসেন!
তাদের গবেষণা পদ্ধতির অন্যতম মৌলিক ত্রুটি হল, তারা যা কিছু প্রমাণ হিসেবে হাজির করার চেষ্টা করেন, সেগুলোর বাস্তব কোনো ভিত্তি থাকে না। তারা প্রতিটি বিষয়ের ارتقائى تعبير বা evolutionary interpretation গ্রহণ করেন।(৩)
প্রাচ্যবিদরা ইসলামী ইতিহাস ও আরবী সাহিত্য থেকে নানা খুচরো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার পর, কিছু ছোটখাটো বিষয় সামনে রেখে একটি মৌলিক নিয়ম বা সার্বিক নীতি তৈরি করে ফেলেন, সামান্য কিছু উদাহরণ দেখে ব্যাপক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান, সীমিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একটি বিষয়ের পুরো কাঠামো তৈরি করে ফেলার চেষ্টা করেন। অথচ এটা দলীল আহরণ ও উপস্থাপনের মারাত্মক ত্রুটি।
পাঠক, প্রাচ্যবিদদের ব্যাপারে এই ফয়সালা আমরা হুট করে গ্রহণ করিনি; বরং তাদের লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও বই-পুস্তক গভীর অধ্যয়ন এবং সুচিন্তিত ও ইনসাফপূর্ণ নির্মোহ পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষণ আমাদের এই স্থির সিদ্ধান্তে নিয়ে এসেছে। তাদের প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধেই এই মৌলিক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। দুয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি–
প্রথম উদাহরণ
কয়েকজন প্রাচ্যবিদ, যেমন গোল্ডজিহার (Goldziher) দাবি করেছেন, গোটা ইসলামী ফিকহ রোমান আইন থেকে সংগৃহীত। প্রমাণ হিসেবে তিনি কিছু সংশয় হাজির করেছেন :
ক. কিছু বিধানের ক্ষেত্রে ইসলামী ফিকহ এবং রোমান আইনের সাদৃশ্য আছে, আবার কিছু আইন হুবহু এক, যেমন এই নীতি–
البينة على المدعى واليمين على من أنكر.
‘প্রমাণের দায়িত্ব অভিযোগকারী পক্ষের, সে ব্যর্থ হলে অভিযুক্ত পক্ষ শপথ গ্রহণ করবে।’
খ. কিছু পরিভাষা উভয় আইনব্যবস্থায় অভিন্ন, যেমন রোমানরা ‘Juris’ শব্দটি হুবহু মুসলিমদের ‘ফিকহ’ (فقه) শব্দের অর্থে ব্যবহার করত, যা বোধ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অর্থ বহন করে।
গ. ইসলামী বিজয়যাত্রার সময়, কায়সারিয়(৪) এবং বৈরুত শহরে রোমান আইনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল এবং কিছু আদালত এই আইন অনুযায়ী পরিচালিত হত। মুসলিমরা যেহেতু আগে কোনো সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত ছিল না, তারা অবশ্যই রোমান আইনি প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবে। (ফাজরুল ইসলাম, আহমাদ আমীন, পৃ. ২৪৬-২৪৭, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, দশম সংস্করণ, ১৯৬৯। সংশয়গুলো নকল করার পর আহমাদ আমীন সেগুলো খণ্ডন করেছেন।)
প্রাচ্যবিদ ড. ব্রোকেলম্যান তার গ্রন্থ ‘তারীখুল আদাবিল আরাবী’তে লিখেছেন–
فلما انتشرت ظلال الإسلام خارج حدود الجزيرة العربية، ودانت لحكمه البلدان والأقطار في المشرق والمغرب، لم يعد العلم بما جاء به الكتاب والسنة كافيا لسد الحاجات العارضة للمسلمين، والقضاء فى كل ما يعِنُّ ويجِدُّ من المسائل والمشاكل المتعلقة بحقوق الناس ومصالحهم...
كان عرف أهل المدينة في الأحكام والتشريع يوافق فى بعض النواحي ما جرى العمل عليه في ولايات المملكة الرومية.
‘যখন ইসলাম আরব উপদ্বীপের সীমানা পেরিয়ে গেল, ইসলামের শাসন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু দেশ ও অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হল, তখন উদ্ভূত নানা প্রয়োজন বা অধিকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর বাণী যথেষ্ট ছিল না...
আইন ও বিচার সম্পর্কিত মদীনাবাসীদের প্রথা বা রীতি কিছু ক্ষেত্রে রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত প্রথার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।’ (তারীখুল আদাবিল আরাবী -জার্মান ভাষা থেকে আরবীতে অনূদিত-, অনুবাদ : ড. আব্দুল হালীম নাজ্জার, দারুল মাআরিফ, কায়রো, পঞ্চম সংস্করণ ৩/২৩৪)
ঘ. (আরেকটি সংশয় হল,) ইসলামী ফিকহ অতি অল্প সময়ে সংকলিত হয়েছে, বহিরাগত আইন দ্বারা প্রভাবিত না হলে এত কম সময়ে এত বড় একটি আইনি সংকলন তৈরি করা কীভাবে সম্ভব!
ঙ. এক গবেষক অদ্ভুত কথা বলেছেন; ইমাম আওযায়ী সংকলিত ফিকহ হারিয়ে না গেলে এই বিষয়ে আরো প্রমাণ পাওয়া যেত! (কারণ তার ধারণা, আওযায়ী রাহ. বৈরুতের রোমান আইন বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেছেন!)
এভাবে এই পণ্ডিতরা (দূরবর্তী) সাদৃশ্য ও (ব্যক্তিগত) ধারণার ভিত্তিতে রোমান আইন থেকে ইসলামী ফিকহ সংগৃহীত হওয়ার দাবি প্রমাণ করার জন্য প্রচুর রেফারেন্স হাজির করলেও ভেবে দেখেননি; এই ধরনের অনুমাননির্ভর কথাবার্তা থেকে বিষয়টি প্রমাণ হওয়া অসম্ভব।
পাঠক, প্রাচ্যবিদদের দাবিগুলোতে যুক্তি ও যৌক্তিকতার অভাব তীব্র ও প্রকট। তারা একটি ব্যাপক ও বড় দাবি করে বসেন, অথচ প্রমাণ হিসেবে ছোটখাট বিষয় ও নিজস্ব অনুমান হাজির করাই যথেষ্ট মনে করেন।
আপনি প্রাচ্যবিদদের যুক্তি বিশ্লেষণ করে দেখুন; প্রায় সবক্ষেত্রে তারা এই অবৈজ্ঞানিক যুক্তির ধারা অনুসরণ করেন। প্রথমে তারা কল্পনায় একটি বিষয় সাজান, এরপর সংশ্লিষ্ট সময়ের ইতিহাস ও সাহিত্য ঘেঁটে যেসব অমৌলিক ও শাখাগত তথ্য তাদের কল্পনার সাথে মিলে যায়, সেগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে বলেন, দেখে নিন, গবেষণা থেকে কী প্রমাণ হল?
দ্বিতীয় উদাহরণ
প্রাচ্যবিদরা প্রতিটি বিষয়ে এই অদ্ভুত দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করেন। যেমন, তারা যখন জাহেলী যুগের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন, তাদের মনে এই ধারণা জন্ম নিল, এটি জাহিলী যুগের সাহিত্য নয়। অনুমান করেই তারা পাকা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন, এই সাহিত্য আসলে হাম্মাদ আর-রাবিয়াহ (حماد الراوية) নিজে তৈরি করে জাহেলী যুগের সাথে সম্বন্ধ করে দিয়েছে! এই অনুমানকে ভিত্তি করে ‘তদন্ত’ চালিয়ে তারা কয়েকটি উদাহরণ খুঁজে পেলেন, যেখানে কিছু ব্যক্তি নিজেরা কবিতা লিখে (জাহিলী যুগের প্রসিদ্ধ কবি) ইমরুল কায়েস বা তারাফার সাথে যুক্ত করে দিয়েছে।
এমন কয়েকটি উদাহরণ দেখিয়ে ভাবখানা এমন, যেন তারা পর্বতসম প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন যে, জাহিলী যুগ সম্পর্কিত গোটা সাহিত্য সম্ভার মনগড়া! এই সাহিত্য ব্যবহার করে কুরআনের বিভিন্ন শব্দের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা ভুল! এর মাধ্যমে প্রাচীন মানুষদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির যে প্রমাণ দেওয়া হয় (তারা হাজারো কবিতা মুখস্থ রাখতেন) এবং (বহু সাহাবী স্মৃতিশক্তিতে) হাদীস সংরক্ষণ করেছেন বলে যে তথ্য পেশ করা হয়, তা-ও ভিত্তিহীন!
এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে মুহাম্মাদ আহমাদ আল-গামরাভীর চমৎকার বই– النقد التحليلي لكتابِ >في الأدب الجاهلي< পড়তে পারেন, সাথে পড়তে পারেন আমীর শাকীব আরসালানের ভূমিকা–
الشعر الجاهلي: أمنحول أم صحيح النسبة؟
তৃতীয় উদাহরণ
কিছু প্রাচ্যবিদ, যেমন প্রফেসর জোসেফ শাখত (Joseph Schacht) এবং প্রফেসর স্মিথ এটি প্রমাণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ– ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে যে সুন্নাহকে গণ্য করা হয়েছে, তা কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকর্মই বোঝায় না, বরং সাধারণ মুসলিমদের জীবনধারাও সুন্নাহর আওতায় আনা হয়েছে। মুসলিম সমাজের সাধারণ প্রথা-প্রচলন থেকেও ইসলামী আইন গৃহীত হয়েছে, যার প্রকৃত শরয়ী ভিত্তি নেই। মিস্টার জোসেফ শাখত লিখেছেন–
Classical theory of Muhammadan law defines sunna as the model behaviour of the Prophet...
But sunna means, strictly speaking, nothing more than ‘precedent’, ‘way of life’...
Margoliouth has concluded that sunna as a principle of law meant originally the ideal or normative usage of the community.
‘মুহাম্মাদী আইন তথা ইসলামী আইনশাস্ত্রের ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব নবীর আদর্শ আচরণ (কর্ম, বক্তব্য ও অনুমোদনকে) সুন্নাহ বলে সংজ্ঞায়িত করে...
তবে সুনির্দিষ্টভাবে সুন্নাহ বলতে কেবলমাত্র পূর্ব থেকে চলে আসা প্রচলিত প্রথা বা ‘জীবনধারা’ বোঝায়...
মার্গোলিওথ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আইনশাস্ত্রের ভিত্তি হিসেবে সুন্নাহ মূলত সমাজের রীতি বা প্রথাগত ধারা বোঝাত।’ (Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, First published 1950, Oxford University Press, p. 58, chap. 7, ‘Sunna, Practice and Living Tradition’)
এই দাবির যুক্তি হল, ‘সুন্নাহ’ শব্দ তখনকার প্রচলিত রীতি-নীতির অর্থে ব্যাপক ব্যবহৃত হত। এই জন্যই আবদুল্লাহ বিন মুকাফফা‘ (যার ইসলাম নিয়েই সন্দেহ ছিল) ‘সুন্নাহ’ শব্দটি এমন অর্থে ব্যবহার করেছেন, যাতে শাসকদের আইনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। শাখত বলেন–
Ibn Muqaffa’, a secretary of state in late Umaiyad and early ‘Abbasid times, subjected the old idea of sunna to sharp criticism.
Anticipating Shafi’i he realized that sunna as it was understood in his time, was based not on authentic precedents laid down by the Prophet and the first Caliphs, but to a great extent on administrative regulations of the Umaiyad government.
In contrast to Shafi’i, however, he did not fall back on traditions from the Prophet but drew the contrary conclusion that the Caliph was free to fix and codify the alleged sunna.
‘ইবনে মুকাফফা‘, যিনি উমাইয়া শাসনের শেষ এবং আব্বাসী শাসনের প্রথমভাগে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন, সুন্নাহ সম্পর্কে প্রচলিত প্রাচীন ধারণার কঠোর সমালোচনা করেন।
তিনি বুঝতে সক্ষম হন, তার যুগে সুন্নাহর যে অর্থ গ্রহণ করা হত, তা নবী এবং প্রথম চার খলীফা থেকে প্রকাশিত বিশুদ্ধ নমুনা (বক্তব্য, কর্ম ও আচরণের) ওপর ভিত্তি করে ছিল না, বরং (সুন্নাহ ও তার চরিত্র নির্ধারণ) অনেকাংশে উমাইয়া আমলের প্রশাসনিক বিধি-বিধানের ওপর নির্ভরশীল ছিল।
ইবনে মুকাফফা‘ শাফেয়ীর বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেন, (ইমাম শাফেয়ী রাহ. বিশ্বাস করতেন, সুন্নাহ নবীজীর বাণী ও কর্মের ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হতে পারে, কুরআনের পর নবীজীর নির্দেশনাগুলোই ইসলামী আইনের চূড়ান্ত ও নির্ভরযোগ্য উৎস)। অপরদিকে ইবনে মুকাফফা‘ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, (প্রশাসনিক পর্যায়ে যে নিয়ম-কানুন বা প্রথাকে) ‘সুন্নাহ’ বলে দাবি করা হয়েছে, তা প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধকরণে (পরবর্তী) খলীফাদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল।’ (The Origins of Mohammadan Jurisprudence, PP. 58-59)
এই হল তাদের চিন্তার পরিক্রমা আর গবেষণার পদ্ধতি, যা দেখে আমাদের মডার্নিস্টরা তাদেরকে ইসলামের মস্ত বড় গবেষক মনে করে।
প্রাচ্যবিদদের পক্ষপাতিত্ব
প্রাচ্যবিদরা আপাত সংযত ও বাহ্যিক বিবেচনায় গুরুগম্ভীর আলোচনা করে বোঝাতে চান, তারা নিরপেক্ষ। কারো মন্দ দিক বলতে চাইলে আগে তার দশটি ভালো গুণ দেখান, যাতে পাঠকের কাছে মনে হবে; তারা নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তির অবস্থা নিরীক্ষণ করছেন, ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ বলছেন।
কিন্তু তাদের লেখা গভীরভাবে পড়লে এই নিরপেক্ষভাব দেখা যায় না, কিছু ক্ষেত্রে তারা বেশ নগ্নভাবে পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব দেখিয়েছেন।
রেইনহার্ট ডোজীর বক্তব্য
খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ ও ঐতিহাসিক ডোজী (Reinhart Dozy) রাখঢাক না রেখে অমুসলিম ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদদের পক্ষপাতিত্ব এবং মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোর কথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন–
(Christians) developed an instructive hatred for the Mussalmans and entertained thoroughly false ideas about Mohammed and the doctrines he preached.
Living in the midst of the Arabs, nothing was more easy than to instruct themselves on the subject: but they refused obstinately to go to the sources which could be found at their doors, and were satisfied with believing and repeating all the absurd fables which they retailed about the Prophet of Mecca.
‘খ্রিস্টানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত বিদ্বেষ ছড়িয়েছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রচারিত শিক্ষা সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত চিন্তা ও ধারণা পোষণ করেছে।
আরবের কেন্দ্রে বসবাস করায় সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা তাদের জন্য সহজ ছিল, কিন্তু তারা একগুঁয়েমি করে নিকটতম উৎস থেকে তথ্য যাচাই করার পরিবর্তে মক্কার নবী সম্পর্কে অর্থহীন ও হাস্যকর সব গাল-গল্প বিশ্বাস করা ও প্রচার করাতেই সন্তুষ্ট ছিল।’ (Syed Ameer Ali, A Short History of the Saracens, Kitab Bhuvan, New Delhi, 1927, p. 487, Chapter XXVI)
ডেনিসন রসের বক্তব্য
ডেনিসন রসও (Edward Denison Ross) স্বীকার করেছেন–
For many centuries, the acquaintance which the majority of Europeans possessed of Muhammadanism was based almost entirely on distorted reports of fanatical Christians.
‘বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপীয়দের ইসলাম সম্পর্কে ধারণা সেইসব মতামতের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছিল, যেগুলো ধর্মান্ধ, অতিশয় গোঁড়া ও পক্ষপাতদুষ্ট খ্রিস্টানরা ছড়িয়ে দিয়েছিল।’
এক লাইন পরেই তিনি লেখেন–
What was good in Muhammadanism was entirely ignored, and what was not good in the eyes of Europe was exaggerated or misinterpreted.
‘ইসলামে যা ভালো ছিল তা পুরোপুরি উপেক্ষিত রাখা হয়েছে, আর যা ইউরোপের দৃষ্টিতে খারাপ ছিল, তা বড় করে তুলে ধরা হয়েছে অথবা তার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।’ (E. Dennison Ross, Introduction to George Sale’s Translation of the Koran, Frederick Warne, London, p. vii)
ব্রোকেলম্যানের বক্তব্য
প্রাচ্যবিদদের লিটারেচারে এই ধরনের পক্ষপাতিত্বের বেশুমার উদাহরণ আছে। কিছু ক্ষেত্রে তারা লজ্জাজনক অসততার আশ্রয়ও নিয়েছে। যেমন, প্রফেসর ব্রোকেলম্যান লিখেছেন–
The Bedouin is above all a purely egotistic individualist. “God have mercy on me and Muhammad, and on no one else besides,” one tradition still permits an Arab convert to Islam to say in prayer.
‘সর্বোপরি বেদুইনরা সম্পূর্ণ স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। (এক বেদুইন দুআ করেছে,) ‘আল্লাহ, আমার এবং মুহাম্মাদের ওপর দয়া করো, আর কাউকে দয়া করো না। একটি হাদীস এখনো ইসলাম গ্রহণকারী একজন আরবকে এমন দুআ করার অনুমতি দেয়।’ (Carl Brockelmann, History of the Islamic Peoples, Translated from German by Joel Carmichael and Moshe Perlmann, Chapter 1: “The Arab and The Arab Empire”, p. 4. 1960, New York.)
পাঠক, একজন আলাভোলা বেদুঈনের এই দুআ হয়তো আপনিও শুনেছেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ শুনে বলেছিলেন–
لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا.
‘তুমি তো আল্লাহর রহমতের বিশালতাকে সংকীর্ণ করে ফেললে!’ (৫)
এই সতর্কবাণী উপেক্ষা করে ব্রোকেলম্যান উল্টো দাবি করে বসলেন, হাদীস শরীফ এই ধরনের দুআ করতে উৎসাহ দিয়েছে!
এই প্রাচ্যবিদদের দেওয়া তথ্য ও চিন্তাই মডার্নিস্টরা গোগ্রাসে গিলেছে এবং তাদের গবেষণায় সীমাহীন মুগ্ধ হয়ে গেছে!
قیاس کن ز گلستان من بہار مرا
‘বাগান দেখে বসন্ত আন্দাজ করে নাও।’
এবার সংক্ষেপে সেই কারণগুলোর দিকে নজর দেওয়া যাক, যেগুলো মডার্নিজম প্রসারে সহায়ক হয়েছে।
মডার্নিজম বিকাশের প্রথম কারণ
মডার্নিজম প্রসারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে ভুলপন্থার শিক্ষাব্যবস্থা। ইসলামী মূল্যবোধ থেকে মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন করে পশ্চিমা চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই পশ্চিমা ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল।
ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের পর ব্রিটিশদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের ইসলামী বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করা, যা ক্রুসেড যুদ্ধগুলোতে মুসলিমদের মজবুত প্রতিরোধ গড়ে তোলার চালিকা শক্তি ছিল। এজন্য তারা প্রথমে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রতি গুরুত্ব দেয় এবং গোটা ভারতবর্ষকে খ্রিস্টধর্মে রূপান্তরিত করার পাঁয়তারা করে।
পাঠক, এটি আমাদের বিদ্বেষমূলক মতামত নয়। কয়েকটি উদ্ধৃতি লক্ষ করুন–
মিস্টার ম্যাংগেলসের বক্তব্য
১৮৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৎকালীন ডিরেক্টর মিস্টার ম্যাংগেলস (Ross Donnelly Mangles) ব্রিটিশ হাউজ অফ কমন্সে বলেছিলেন–
Providence has entrusted the extensive Empire of Hindustan to England in order that the banner of Christ should wave triumphant from one end of India to the other. Everyone must exert all his strength that there may be no dilatoriness on any account in continuing in the country the grand work of making all India Christian.
‘ঈশ্বর ইংল্যান্ডের হাতে হিন্দুস্তানের সুবিশাল সাম্রাজ্য তুলে দিয়েছেন, যাতে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যীশুখ্রিস্টের বিজয়ী পতাকা উড়তে পারে। সবাইকে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে, যাতে পুরো ভারতবর্ষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার এই মহৎ কাজে ঢিলেমি না হয়।’ (Vinayak Damodar Savarkar, The Indian War of Independence of 1857, p. 55, 1909)
রেভারেন্ড কেনেডির বক্তব্য
এই সময় মিশনারিরা ভারতবর্ষকে খ্রিস্টধর্মে রূপান্তর করার প্রতিজ্ঞা করে। রেভারেন্ড কেনেডি (কবহহবফু) অকপটে লিখেছিলেন–
Whatever misfortune come on us as long as our Empire in India continues, so long let us not forget that our chief work is the propagation of Christianity in the land. Until Hindustan from Cape Comorin to the Himalayas, embrace the religion of Christ, and until it condemns the Hindu and the Muslim religions, our efforts must continue persistently.
For this work we must make all the efforts we can and use all the power and all the authority in our hands; and continuous and unceasing efforts must be kept on until India becomes a magnificent nation, the bulwark of Christianity in the East!
`ভারতবর্ষে আমাদের সাম্রাজ্য যতদিন টিকে আছে, ততদিন যত বিপদই আসুক না কেন; আমাদের ভুললে চলবে না, আমাদের প্রধান কাজ হল এই দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা। যতদিন না (দক্ষিণের) কন্যাকুমারী থেকে (উত্তরের) হিমালয় পর্বতমালা পর্যন্ত গোটা হিন্দুস্তান খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করছে, হিন্দু-মুসলিম স্ব স্ব ধর্ম ত্যাগ করছে, আমাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।
এই কাজের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে এবং সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ব্যবহার করতে হবে। যতদিন ভারতবর্ষ একটি গৌরবময় জাতি হয়ে না উঠছে এবং প্রাচ্য খ্রিস্টধর্মের শক্তিশালী দুর্গে পরিণত না হচ্ছে, আমাদের নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই।' (The Indian War of Independence, p. 56)
চ্যাটেলিয়ারের বক্তব্য
ব্রিটিশদের এই প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সফল না হলেও শিক্ষিত মুসলিম সমাজকে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল। কীভাবে তারা এ কাজে সফল হল? খ্রিস্টান মিশনারীর একটি ফরাসী ম্যাগাজিনে মিস্টার চ্যাটেলিয়ার (Chatelier) লিখেছেন–
No doubt our missionaries have failed so far indirectly undermining the faith of the Muslims. This end can be achieved only by the propagation of ideas through the medium of languages. Through the spread of these languages, the world of Islam could be brought in contact with European Press and paths would be paved for the material progress of the Muslims.
Thus, the missionary organisations would realize their goal of destroying Islamic religious concepts which so far have preserved their identity and strength in isolation and separatism.
`সন্দেহ নেই, এখন পর্যন্ত আমাদের মিশনারী সংগঠনগুলো মুসলিমদের বিশ্বাসের ভিত দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে আমাদের চিন্তাগুলো ইউরোপীয় ভাষার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হলে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। এই ভাষাগুলো প্রচারের মধ্য দিয়ে ইউরোপের সঙ্গে ইসলামী বিশ্বের সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে এবং মুসলিমদের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে।
এভাবে মিশনারী সংস্থাগুলো তাদের উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবে, তথা ধর্মীয় চিন্তাগুলো ধ্বংস করতে পারবে, যেগুলো শত বিচ্ছিন্নতা ও বিভাজনের মাঝেও এতদিন মুসলিমদের স্বতন্ত্র পরিচয় ও শক্তির জায়গা ধরে রেখেছে।'
তিনি লেখেন–
The political break-up of the world of Islam will open the way to Europe’s civilizing mission. It is inevitable that the Muslims will degenerate politically, and before long the world of Islam will become like a city surrounded by European barbedwire entanglements.
`ইসলামী বিশ্বের রাজনৈতিক পতন ইউরোপের সাংস্কৃতিক মিশনের দুয়ার খুলে দেবে। এটি অনিবার্য সত্য, মুসলিমরা রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং শীঘ্রই ইসলামী বিশ্ব পশ্চিমা কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা এক নগরে পরিণত হবে।'
তিনি আরো লেখেন–
It is not to be expected that the Muslims in general would be able to bring forth new positive attitudes and new social qualities, once they have given up their present attitudes and qualities.
With the weakening of their belief in Islam, decay and disintegration are bound to set in: and when this decay and this disintegration spreads throughout the world of Islam, the religious spirit of the Muslims will be entirely uprooted and will never be able to re-emerge in a new form.
`একবার মুসলিমরা তাদের বিদ্যমান চিন্তা-বিশ্বাস ও গুণাবলি ত্যাগ করলে আগামীতে নতুন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বা সামাজিক গুণাবলি গড়ে তোলার সাধারণত আশা করা যায় না। ইসলাম সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে গেলে অবক্ষয় ও ভাঙন অবধারিত। এই অবক্ষয় ও ভাঙন পুরো ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে মুসলিমদের ধর্মীয় চেতনা ধ্বংস হয়ে যাবে, তা নতুন করে জাগ্রত হতে পারবে না।' (Islam and the West, pp. 13-15, citing a quotation from sheikh Said Ramadan al-Bouti Rah. in an article published in Al-Muslimoon and The Voice of Islam, Karachi, October 1957)
পাঠক লক্ষ করেছেন, ব্রিটিশদের ভারত বিজয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল? সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কোন্ পথ ও পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল?
লর্ড ম্যাকাওলের বক্তব্য
এই মিশনারী পরামর্শ মেনে ইউরোপীয় ভাষা প্রচলন এবং ইউরোপীয় চিন্তা-ধারার প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ১৮৩৫ সালে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এটির সভাপতি ছিলেন প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি লর্ড ম্যাকাওলে (Lord Macaulay), যিনি তাঁর প্রতিবেদনে স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন–
We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and color, but English in tsate, opinions, words and intellect.
`আমাদের এমন একটি শ্রেণি গড়ে তোলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত, যারা কোটি কোটি ভারতীয় প্রজার মাঝে আমাদের প্রতিনিধিত্বকারী হবে। এই শ্রেণির লোকেরা রক্ত ও গায়ের রঙে হবে ভারতীয়, কিন্তু রুচি-স্বভাব, চিন্তা, ভাষা ও বুদ্ধিতে হবে পুরোদস্তুর ইংরেজ।' (Basu, Major Baman Das, History of Education in India under the Rule of the East India Company, The Modern Review Office, Calcutta, Chapter: “Education in India (1833–1853)”, p. 87)
লর্ড ম্যাকাওলের এই বক্তব্য এখন বাস্তব সত্য। সন্দেহ থাকলে সেই লোকদের হাল দেখুন, যারা এই শিক্ষাব্যবস্থায় পড়াশোনা করে পশ্চিমা ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়েছে আর এখন দাবি করছে, আমরা যেন পুরোনো ইসলাম বাদ দিয়ে আমাদের সময়ে ইসলামের নতুন সংস্করণ গ্রহণ করি।
ক্যান্টওয়েল স্মিথের বক্তব্য
প্রফেসর উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথও পশ্চিমা শিক্ষার এই গভীর প্রভাব স্বীকার করেছেন। তিনি মডার্নিজমের প্রসার ও প্রভাবের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন–
Much of the West came to the Muslim world, again, not least its educational institutions rearing indigenously a generation deeply exposed to Western modernity.
`পশ্চিমা সভ্যতার বহু দিক মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রবেশ করেছিল, বিশেষত পশ্চিমা একাডেমিক কাঠামো স্থানীয়ভাবে একটি প্রজন্ম তৈরি করছিল, যারা পশ্চিমা মডার্নিটির (পশ্চিমা চিন্তা-ভাবনা, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের) গভীর সংস্পর্শে এসেছিল।' (Smith, Wilfred Cantwell, Islam in Modern History, Princeton University Press, 1957, Chapter: “Islam in Recent History”, p. 57)
যে মেধাবী মুসলিম যুবকরা জাতির গর্ব ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল, এই শিক্ষাব্যবস্থা তাদের মন-মানস পরিবর্তন করে দিয়েছে। আজ তাদের চিন্তা-কর্মে ইসলাম সঠিকরূপে ফিট হচ্ছে না, তারাও সাধারণ মুসলিম সমাজের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছে না। আল্লামা ইকবাল রাহ. সত্যিই বলেছেন–
فرنگی شیشہ گر کےفن سے پتھر ہو گئے پانی
মডার্নিজম বিকাশের দ্বিতীয় কারণ
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তো ছিল এই শিক্ষাব্যবস্থা। তবে মডার্নিজম প্রসারের পেছনে আমাদেরও কিছু দুর্বলতা ছিল। আমরা চোখের সামনে মডার্ন চিন্তার প্রসার হতে দেখেছি, কিন্তু এর সমাধানে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে পারিনি। কিছু পদক্ষেপের কথা তুলে ধরছি।
ক. এই সময়ে আলেম সমাজে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাদের নিষ্ঠা ও খোদাভীরুতা বহু মানুষকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দিকে আকর্ষণ করেছিল। তবে প্রয়োজন ছিল নতুন উদ্যোগ গ্রহণের, যা ইমাম গাযালী ও ইমাম রাযী আপন সময়ে গ্রহণ করেছিলেন। প্রয়োজন ছিল এমন পুনর্জাগরণ, যা মডার্নিজমের কুপ্রভাবকে গোড়া থেকেই দমন করতে পারত।
প্রয়োজন ছিল আলেমদের এক চৌকষ দল, যারা আধুনিক দর্শন -যা পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তি- বিশ্লেষণ করবেন, পশ্চিমা চিন্তাধারার পর্যালোচনামূলক গভীর অধ্যয়ন করবেন, পশ্চিমা চিন্তকদের গতি-প্রকৃতি ধরতে পারবেন, পশ্চিমা চিন্তাগুলোকে কুরআন-সুন্নাহর অতুলনীয় মানদণ্ডে যাচাই করে, যুক্তির সাহায্যে এর প্রকৃত হাল স্পষ্ট করবেন, যেমন ইমাম গাযালী, ইমাম রাযী গ্রিক দর্শনের স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন।
খ. অন্যদিকে, পশ্চিমা সভ্যতার ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবেলায় আমাদের উচিত ছিল বৈশ্বিক ঘটনাবলির প্রতি তীক্ষ্ম নজর রাখা, ইসলামের ভাবধারাকে নতুন যুগের মানসিকতার সাথে মিল রেখে ইতিবাচক উপস্থাপন করা, বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে মানুষকে বলা; ইসলাম কখনো ধূলিমলিন হয়নি, আজও তা নতুন আছে, চিরকাল জীবন্ত ও তরতাজা থাকবে। প্রথম শতাব্দীর সমস্যাগুলোর সমাধান যেমন ছিল এখানে, একুশ শতকের সমস্যার সমাধানও এখানে আছে। যুগের এমন কোনো সমস্যা নেই, যা ইসলাম অসাধারণ উপায়ে ডিল করতে পারে না।
গ. আমাদের উচিত ছিল দাওয়াহ ও ইসলাম প্রচারের কাজে প্রজ্ঞাপূর্ণ উপায় অবলম্বন করা, আধুনিক সভ্যতার প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা, যেমন প্রথম যুগের মুসলমানরা রোম ও পারস্যের সভ্যতা পরখ করেছিলেন।
ঘ. দরকার ছিল মুসলিমদের জন্য উপকারী হতে পারে এমন সব উপায় ও কৌশল শেখা, যেমন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নতুন যুদ্ধাস্ত্র ও হাতিয়ার নির্মাণের কৌশল শিখতে উৎসাহ দিয়েছিলেন।
কিন্তু আমরা কোনোটাই করিনি। আমরা অ্যারিস্টটল (Aristotle) এবং প্লেটোর (Plato) দার্শনিক মতামত নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছি, তবে আধুনিক দর্শনের প্রাথমিক বিষয়েও অজ্ঞ রয়ে গেছি। মানুষকে বলেছি, পশ্চিমের বিষাক্ত দর্শনে প্রভাবিত হয়ো না, কিন্তু বিষের প্রকৃতি কী, এর পরিষ্কার জবাব আমাদের কাছে ছিল না।
আমরা পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণ করার লাভ-ক্ষতি এবং সেইসব সমস্যার ব্যাপারে বিলকুল বেখবর ছিলাম, যেগুলোর কারণে আমাদের জাতি ক্রমশ পশ্চিমা সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমরা শুধু বলে গেছি, পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণ করো না, এটা কুফর ও অবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু কেন এটি অবিশ্বাস? পশ্চিমা দর্শন বর্জন করে বর্তমান যুগে ইসলাম কীভাবে মানবতার সঠিক দিশা দেখাচ্ছে, এই প্রশ্নের উত্তরও আমাদের কাছে ছিল না।
আমরা পশ্চিমা সভ্যতার সামগ্রিক বিশ্লেষণ করিনি, যা থেকে আমরা উপকারী দিকগুলো গ্রহণ করতে পারি এবং পৃথিবীকে বোঝাতে পারি; আমরা বিশেষ কোনো সভ্যতার বিরুদ্ধে নই, কেবল ইসলামবিরুদ্ধ ও সুস্থ যুক্তি-বিরুদ্ধ যা কিছু আছে, আমরা সেটাই প্রত্যাখ্যান করি। এই অজ্ঞতার ফলে আমরা যুগের নতুন নতুন উন্নতি ও পরিবর্তনগুলোকে ইসলামবিরোধী গণ্য করেছি, আর এভাবে ইসলামের ভুল উপস্থাপন করেছি।
ঙ. মনে রাখতে হবে, উন্নয়ন ও সংস্কারের শ্লোগান নিয়ে যে আন্দোলনগুলো মাথাচাড়া দিচ্ছে, সেগুলোকে কেবল কাফের বা অবিশ্বাসী বলে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয়, এই মনোভাব বরাবরই বিপদ ডেকে এনেছে।
আজ থেকে তিন শতাব্দী আগে খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধেও এমন সংস্কার ও পরিবর্তনের আন্দোলন উঠেছিল। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের শক্তিশালী ভিত না থাকায় তারা যুক্তির মাধ্যমে সঠিক জবাব দিতে পারেনি, বরং `নাস্তিক' ও `বিধর্মী' ট্যাগ দিয়ে আন্দোলন দমাতে চেয়েছিল। যখন ক্ষমতা ধর্মের হাতে ছিল, তখন এমন 'বিধর্মী' ও `নাস্তিকদের' কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। জন হাস (John Huss) এবং জেরোমের (Jerome) মতো বিখ্যাত খ্রিস্টান মডার্নিস্টদের সংস্কারের দাবি তোলার অপরাধেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, কিন্তু আন্দোলন থেমে থাকেনি; শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টধর্মের ধ্বংস ডেকে এনেছিল।
সম্প্রতি তুরস্কে আরেকটি উদাহরণ দেখা গেছে। সেখানে পশ্চিমা চিন্তা ও ইসলামের মধ্যে যখন তীব্র সংঘাত চলমান, আলেমরা তখন কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এমনকি সুলতান সেলিম সেনাবাহিনীকে নতুন ধাঁচে সংগঠিত করা এবং আধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করার পরিকল্পনা করলে আলেমরা এই সিদ্ধান্তকে ইসলাম-বিরোধী ঘোষণা করেছিলেন।
ফলে মডার্নিস্ট গোষ্ঠী, যারা আগেই ধর্মের প্রতি ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছিল, ইসলাম থেকে আরো দূরে সরে গেল এবং তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল, ধর্মই উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় কাঁটা। পরবর্তী সময় মুস্তফা কামাল পাশা ক্ষমতায় এলে ইসলামের বুনিয়াদ ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়, যে বেদনাদায়ক ইতিহাস সবাই জানেন।
চ. আমাদের কর্তব্য, সর্বদা ইসলামকে যুগের উন্নতির সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থাপন না করা। বরং এই সত্য প্রচার করা; ধর্ম ও উন্নতি একে অপরের পরিপূরক; ইসলামকে উপেক্ষা করে উন্নতি সম্ভব নয়, ইসলাম অনুসরণ করেই প্রকৃত উন্নতি অর্জন করা সম্ভব। ইতিহাস এর সবচেয়ে বড় সাক্ষী।
–মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দারুল উলূম করাচি, ৩
পহেলা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ ঈসায়ী
[ভাষান্তর : মাওলানা আবু আনাস মুহাম্মাদ সালমান]
(সমাপ্ত)
টীকা
১. (David De Santillana), ইটালির রোম ইউনিভার্সিটির History of the Political and Religious Institutions of Islam বিভাগের প্রফেসর ছিলেন। তার প্রবন্ধের শিরোনাম, খধি Law and Society । আর The Legacy of Islam হল প্রাচ্যবিদদের লেখা ১৩টি প্রবন্ধের বিখ্যাত সংকলন।
২. কুরআনই ইসলামী আকীদার সবচে মৌলিক ও প্রামাণ্য উৎস, মদীনা সনদ ছিল মদীনায় বসবাসকারী সব পক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকার রক্ষার চুক্তিপত্র, এতে আকীদা-বিশ্বাসের আলোচনা উদ্দেশ্য ছিল না, তাই এখানে মদীনা সনদের কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক।
৩. অর্থাৎ ইসলামী কোনো নীতি বা আইনকে মানবসমাজের পরিবর্তন ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্লেষণ করেন, ইসলামের ব্যাখ্যায় বর্তমানের প্রাসঙ্গিকতাকে প্রাধান্য দেন।
৪. বর্তমান তুরস্কের মধ্য আনাতোলিয়ার অংশ, প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে ক্যাপাডোসিয়া (Cappadocia) প্রদেশের রাজধানী ছিল।
৫. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৮০; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৪৭; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ২৯৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭২৫৫। ইমাম তিরমিযী রাহ. হাদীসটিকে ‘সহীহ’ বলেছেন।
৬. বর্তমান ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত, তামিলনাড়ু রাজ্যের অংশ।