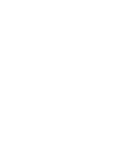ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসন : একটি সমীক্ষা
প্রফেসর ড. আনওয়ার-উল করিম
ভারতে মুসলিমদের আবির্ভাবের পূর্বে এ উপমহাদেশের সাহিত্যে ‘হিন্দু’ শব্দটির প্রচলন ছিল না। অষ্টম শতকের প্রারম্ভে মুসলিম আরবেরা সিন্ধুতে আগমন করেন এবং এর নামকরণ করেন হিন্দ। তারা এখানকার জনগণকে ‘হিন্দী’ বলে আখ্যায়িত করেন। ক্রমে ‘হিন্দ’ শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশই ‘হিন্দ’ নামে পরিচিত হয়ে উঠে। এখন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নিজেদেরকে ‘হিন্দু’ বলে পরিচয় দেয়। ভারতীয় দর্শনের ছয়টি আদি মতবাদ ছাড়াও চার্বাকের অবিমিশ্র নিরীশ্বরবাদ, আচার্য রামানুজের দ্বৈতবাদ, আচার্য শংকরের সর্বেশ্বরবাদ (যা অদ্বৈতবাদেরই অনুসিদ্ধান-), রাজা রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদ এবং বহুদেববাদও হিন্দু-ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে হিন্দু ধর্ম হল কতকগুলো পরস্পরবিরোধী ধর্মীয় মতবাদ ও দর্শনের সমষ্টি।
‘হিন্দুবাদ’ হচ্ছে কঠোর বর্ণাশ্রমভিত্তিক একটি সমাজ-ব্যবস্থা, যাতে মানুষের মর্যাদা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সুবিচারের কোনো স্বীকৃতি নেই। এই সমাজ-কাঠামোর দার্শনিক ভিত্তি হল জন্মান-রবাদ। একজন ব্রাহ্মণ পূর্বজন্মে পুণ্যবান ছিল বলেই এখন ব্রাহ্মণরূপে জন্মলাভ করেছে এবং একজন অস্পৃশ্য পূর্বজন্মে পাপী-জীবন যাপন করেছে বলেই এখন অস্পৃশ্য হয়ে জন্মেছে। অস্পৃশ্যকে নিজের মুক্তির জন্যে অবশ্যই দাসের মতো ব্রাহ্মণের পূজা ও সেবা করতে হবে। যারা হিন্দু বর্ণাশ্রমকে মেনে নিয়েছে তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে স্থান পেয়েছে। পক্ষান্তরে যারা তা মানেনি তাদেরকে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের অধিপত্য মেনে নেয়নি। এর ফলে তাদেরকে মাতৃভূমি ত্যাগ করে সুদূর প্রাচ্যে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। দ্রাবিড়, শক ও হুনদের সমবায়ে হিন্দু বর্ণাশ্রমের নিম্নতম বর্ণটি গঠিত, যাদের বলা হয় শুদ্র ও অস্পৃশ্য। আর এখন ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে বলা হয় ‘হরিজন’। মুসলিমরা সাত শতাব্দীরও অধিক কাল এ উপমহাদেশ শাসন করেছে। শিখরা প্রসার লাভ করেছে মুসলিম ও ব্রিটিশদের শাসনামলেই। কাজেই শিখদেরকে ব্রাহ্মণ্যবাদ মেনে নিতে বাধ্য করার অথবা উৎখাত করার ক্ষমতা ব্রাহ্মণদের ছিল না। তাই একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী একজন শিখ।
যারা বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে না, হিন্দুরা কখনো তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা ভাবতে পারে না। অতএব হিন্দুবাদ বলতে বোঝায় হিন্দু-সমাজ, অপেক্ষাকৃত মার্জিত ভাষায় আর্য-সমাজ। আর্য-সমাজের বিশিষ্ট নেতা লালা হরদয়াল আর্য-সমাজের মূলনীতি ঘোষণা করেছিলেন এবং ১৯২৪ সালের ২০ জুনের ‘তেজ’ পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। লালাজী বলেছিলেন, ‘হিন্দুদের ভবিষ্যৎ চারটি স্তম্ভের উপর স্থিত। এগুলো হচ্ছে : ১. হিন্দুবাদ সুসংহতকরণ, ২. হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা, ৩. মুসলিমদেরকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিতকরণ, ৪. আফগানিস্তান ও উপমহাদেশের সংলগ্ন অন্যান্য দেশ বিজয়।’-আল্লামা আবুল হাশিম : হিন্দু জাতীয়তাবাদ
এম.কে. গান্ধী ১৯২১ সালে তার প্রকাশিত Young India পত্রিকায় লিখেছিলেন, ‘আমি বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাস করি, আমি গো-রক্ষাকে ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ বলে মনে করি এবং মূর্তিপূজায় অবিশ্বাস করি না।’
কেউ কেউ মনে করেন, ভারত আজ হিন্দুবাদ বর্জন করেছে। এ ধারণা ঠিক নয়। হিন্দুবাদের যুগ যুগ পুরানো ভাবধারার প্রভাব এখনো সুদূরপ্রসারী। সমাজের বহিরঙ্গে দৃশ্যমান হিন্দুদের তথাকথিত উদারনৈতিকতা তাদের সমাজের সত্যিকার পরিচয় নয়। এই উদারনৈতিকতার অন্তরালে লুকিয়ে আছে আর্য-সমাজের সত্যিকার রূপ। বর্ণশ্রমভিত্তিক হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী ‘আর্য-সমাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর বিদেশ-সফরে পাচক সাথে নেওয়ার ঘটনাতো সর্বজনবিদিত। সফর ব্যপদেশে তিনি মিসরীয়, ইংরেজ ও রুশদের সাথে বিভিন্ন বৈঠক ও আলোচনায় মিলিত হয়েছেন, কিন্তু তাদের সাথে পানাহার করেননি। তিনি সর্বপ্রযত্নে হিন্দুবাদের যুগপ্রাচীন শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও গোড়ামিকে রক্ষা করেছেন, যা কঠোর বর্ণাশ্রম তথা মানুষের সাম্যের অস্বীকৃতি থেকে গড়ে উঠেছে।
মহারাষ্ট্রনেতা বালগংগাধর তিলক তার রায়গড়-বক্তৃতায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, এ উপমহাদেশের মুসলিমরা হচ্ছে বিদেশী লুঠেরা। সুতরাং তাদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। বালগংগাধর তিলক মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।
হিন্দুরা ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী। এ ধর্মবিশ্বাস শিখ, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির ধর্মবিশ্বাস থেকে স্বতন্ত্র। খৃষ্টীয় ১৯০০ সালে এ উপমহাদেশের হিন্দুরা দ্বারভাঙ্গার মহারাজার নেতৃত্বে ‘ভারত মহামণ্ডল’ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। এই সংগঠনের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল বাল গংগাধর তিলকের রাজতৈনিক দর্শনেই অনুরূপ। তিলকের মানবতাবিরোধী মতবাদকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে তার অনুসারীরা তাকে ‘লোকমান্য’ উপাধীতে ভূষিত করেছিলেন। ‘ভারত মহামণ্ডল’ তার সত্যিকার স্বরূপ সর্বসাধারণের সমক্ষে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত এর সপ্তম অধিবেশনে নতুন নাম গ্রহণ করে ‘হিন্দু মহাসভা’। বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা ডক্টর মুনজী হিন্দু মহাসভার ১৯২৩ সালের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন, ‘ইংল্যান্ড যেমন ইংল্যান্ডবাসীদের, ফ্রান্স যেমন ফরাসীদের এবং জার্মানী যেমন জার্মানদের তেমনি ভারতও হিন্দুদের।’ ১৯১৩ সালে অপর একজন কংগ্রেসনেতা বাংলার বিপিন চন্দ্র পাল বলেছিলেন, ‘ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এখনো পর্যন্ত মুখ্যত একটি হিন্দু আন্দোলন।’ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দমঠ’ পুস্তকে বিধৃত রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল সর্বতোভাবে একটি হিন্দু আন্দোলন। বঙ্কিম চন্দ্র ‘গীতা’-কে এ আন্দোলনের নৈতিক, আত্মিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিরূপে উপস্থাপিত করেন। বঙ্কিমের ‘আনন্দমঠ’ স্বাধীনতা অর্জনের অপরিহার্য পূর্বশর্তরূপে মুসলিমদের উৎখাত তথা নিমূর্ল করার আহ্বান জানায়। বঙ্কিম চন্দ্র আজ ভারতে ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রূপে সমাদৃত। এই তো ভারতের জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ! (আবুল হাশিম : হিন্দু জাতীয়তাবাদ)।
এ উপমহাদেশের মুসলিমরা ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত এক শত বছরেরও বেশি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়েছে। এরপর অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের বলে তাদেরকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে ফেলা হয়েছে। মুসলিমদের সেই সংগ্রামকালে হিন্দুরা এ উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসনকে কায়েমী করার জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সেই সময়ে মুসলিমরা যে অমানবিক নির্যাতন ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল তার তুলনায় কয়েকজন ক্ষুদিরামের ফাঁসি ও কয়েকটি জহরলালের কারাবাস উল্লেখ করার মতো কোনো বিষয় নয়। এই ঢাকারই ভিক্টোরিয়া পার্কে (যা বর্তমানে শহীদ পার্ক নামে পরিচিত) যুগপৎ ষাটজন মুসলিমকে গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাদের মৃতদেহ মাসের পর মাস একই অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। উইলিয়াম হান্টার ১৮৭১ সালে প্রকাশিত তার `The Indian Musalmans’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘এক শত সত্তর বছর আগে বাংলার একজন অভিজাত মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া সম্ভব ছিল না। বর্তমানে তার পক্ষে ধনী থাকা প্রায় অসম্ভব।’ একই গ্রন্থের `The wrongs of the Muhammedans under British Rule’ শীর্ষক অধ্যায়ে উইলিয়াম হান্টার মুসলিমদের প্রতি ব্রিটিশদের অত্যাচারের ফিরিস্তি দিয়েছেন। নিম্নে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। ‘তিনটি বিশেষ উৎস থেকে নিরন্তর অর্থ আসতো একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ধনভাণ্ডারে। এ উৎসগুলো হল সামরিক আধিপত্য, রাজস্ব আদায়ের অধিকার এবং বিচার বিভাগীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। কিন্তু এখন সামরিক চাকুরিতে তাদের কোনো প্রবেশাধিকার নেই, বেসামরিক চাকুরির ক্ষেত্রেও মুসলিমদের একচেটিয়া আধিপত্যের কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই। আইন ব্যবসায়ে এখন মুসলমান খুঁজে পাওয়া কঠিন, অথচ এক কালে আইন ব্যবসা ছিল সম্পূর্ণ মুসলমানদেরই করায়ত্ব। চিকিৎসাবৃত্তির বেলায়ও একই কথা।
১৮২৮ সালে Resumption পাশ হয়। উইলিয়াম হান্টার বলেন, ‘এই আইনের বলে শত শত প্রাচীন পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়, মুসলমানদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, যা রাষ্ট্রের সম্পত্তির আয় দ্বারা পরিচালিত হতো।’
হান্টার সাহেব আরো বলেন, ‘সরকারী চাকুরী ও মঞ্জুরীযোগ্য বিভিন্ন বৃত্তির দ্বারও মুসলিমদের জন্যে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এভাবে হিন্দুদের সক্রিয় সহযোগিতায় মুসলিমদেরকে সর্বস্বান্ত করে দেওয়া হয়, যারা সাত শতাব্দীরও অধিককাল এ উপমহাদেশ শাসন করেছে। পক্ষান্তরে হিন্দুরা তাদের নতুন প্রভু ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধীরে ধীরে স্ফীত হয়ে ওঠে।’
সিপাহী বিপ্লবকালে ১৮৫৬-১৮৫৭ সালে বাংলাদেশে একটি নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছিল। এদের নব্য জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বিপ্লবী সিপাহীদের বা তাদের অনুগামী আমজনাতার কোন উদ্দেশ্যগত বা স্বার্থগত সামঞ্জস্য ছিল না। জাতীয়তার প্রথম উদ্বোধন পর্বে এ দেশের নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ইংরেজের আশ্রয়েই ধীরে ধীরে নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার বিস্তৃত করতে চেয়েছিল, হঠাৎ গণ-বিপ্লব বা রাজ-বিদ্রোহের রণঝংকারে দিল্লীর মসনদ তারা দখল করতে চায়নি।
একপর্যায়ে ব্রিটিশ কূটনীতিকরা তাদের ভারতীয় বন্ধুদেরকে তথা হিন্দুদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল যাতে উপমহাদেশে ব্রিটিশ-শাসন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে হিন্দুদের নিশ্চিত সমর্থন লাভ করা যায়। ভারতের তদনীন্তন বড় লাট লর্ড ডাফরিনের নির্দেশে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ কর্মচারী এলান ওক্টোভিয়ান হিউম ১৮৮৫ সালে ‘ভারতীয় কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠা করেন। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন ডব্লিউ.সি. বেনার্জি। পাঁচজন ব্রিটিশ নাগরিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন; ১৮৮৮ সালে কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জর্জ ইউল, ১৮৮৯ সালে বোম্বাই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্যার ডব্লিউ.ওয়েডারবার্ণ, ১৮৯৪ সালে মাদ্রাজ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আলফ্রেড ওয়েভ, ১৯০৪ সালে বোম্বাই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্যার হেনরী কটন, ১৯১০ সালে এলাহাবাদ অধিবেশনে দ্বিতীয়বার সভাপতিত্ব করেন স্যার ডব্লিউ.ওয়েডারবার্ণ এবং ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এনি বেসান-।
ব্রিটিশ সরকারের প্রতিভূরূপে এলান ওক্টোভিয়ান হিউম কংগ্রেসের ভবিষ্যত-কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। উপমহাদেশের ইতিহাসে তিনিই প্রথম প্রচার করেন ‘ভারতীয় জাতীয়তা’র বাণী। ১৮৮৯ সালে তিনি ঘোষণা করেন, ‘ভারতবাসীরা ভারতীয়ই’। ভারতে কোনো সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব আছে বলে তিনি স্বীকার করেননি। সুতরাং কংগ্রেসের আদি পরিচয় থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, কংগ্রেসের নীতি ব্রিটিশবিরোধী ছিল না; বরং তা ছিল শতকরা এক শত ভাগ ব্রিটিশপন্থী। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্যার সুরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলার স্বদেশী আন্দোলন এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন ছিল না, তা ছিল লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন শুরু করে ১৯১৯ সালে, প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরে।
দুই.
পশ্চিমবঙ্গে যেদিন পহেলা বৈশাখ হয় কয়েক বছর যাবৎ তার একদিন আগে পহেলা বৈশাখ হয় বাংলাদেশে। এ উপলক্ষে পান্তা-ইলিশের ধুম পড়ে যায়। গণমাধ্যমের প্রচার-প্রচারণা এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক তৎপরতা এসব বিষয়কে ভীষণভাবে উৎসাহিত করে। অথচ এভাবে বাঙালী হওয়ার সুযোগ অনেকেরই নেই। আর পহেলা বৈশাখের উচ্চমূল্যের পান্তা-ইলিশ খেয়ে বাঙালী সাজার নিশ্চিত আর্থিক সংস্থানও এদেশের অধিকাংশ মানুষের নেই। এভাবে কিংবা অন্য কোনো ভাবে বাঙালী সাজার সুযোগ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদেরও নেই। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবেশী সমাজ সেখানকার বাংলাভাষী মুসলমানদের কখনো বাঙালী নয়, মুসলমানই বলেন এবং তাদেরকে সমাজের বাইরের মানুষ হিসেবেই দেখেন। সেখানে মূলত বাংলাভাষী হিন্দুরাই কেবল নিজেদের বাঙালী বলেন। তারা অবশ্য একই সঙ্গে বাঙালী, ভারতীয় এবং হিন্দু। আর মুসলমানরা যে ভাষাতেই কথা বলুন কিংবা যে প্রদেশেরই অধিবাসী হন, তারা কেবল মুসলমান। এটাই সেখানে বাস্তবতা। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান হওয়ার পর এখানকার বাংলাভাষী মুসলমানরা অনেকেই বাঙ্গালী হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এখানকার প্রতিবেশী সমাজও এতদঞ্চলের বাংলাভাষী মুসলমানদের বাঙালী হিসেবে দেখতে চান। এর কারণটা এই যে, হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী মুসলমানদের বাঙালী হিসেবে দেখলে তাদের সমান দৃষ্টিতে দেখার প্রয়োজন হবে এবং সমান সুযোগ-সুবিধাও দিতে হবে। পক্ষান্তরে মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশে মুসলমানদের বাঙালী হিসেবে অভিহিত করতে পারলে তাদেরকে ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, আদর্শ ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে অমুসলিম বানানো যাবে কেবল তাই নয়, বাংলাভাষী মুসলমানদের সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় থাকবে না। এটা অবশ্য মূল এবং একমাত্র কারণ নয়। এর মূল কারণটা হল, তারা চান যে, এখানে মুসলমারা তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙালী সংস্কৃতি তথা হিন্দু সংস্কৃতি গ্রহণ করুক। এটা আসলে একটি জাতির নিজস্ব আদর্শ ও সংস্কৃতি ক্রমে বদলে দেয়ারই একটা কৌশল। কেননা, একজাতিতত্ত্বের ধারণায় স্থির থাকার কারণে প্রতিবেশী সমাজ এখনো বিভিন্ন ধর্মীয় সমপ্রদায়ের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করেনি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখে সবার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার কোনো উপায়ও তাদের জীবন-ব্যবস্থায় নেই। সমস্যা এখানে ধর্ম বা ধর্মীয় সংস্কৃতি নয়, মূল সমস্যা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সমপ্রদায়ের মুষ্টিমেয় লোকের অতিরিক্ত সুযোগ পাওয়ার সুবিধার্থে এবং অন্য ধর্মের গণমানুষকেও নিজ ধর্মের নিম্নবর্ণের সিংহভাগ মানুষকে বঞ্চিত করার জন্য এবং অন্য ধর্মের মানুষদের প্রতি বৈরী করে রাখার প্রয়োজনে নানা কূটকৌশলে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার।
পশ্চিমবঙ্গের গণমানুষের কাছে পহেলা বৈশাখ বলতে বোঝায় হালখাতার দিন। মুসলমান ব্যবসায়ীরা হালখাতা করেন নিজস্ব ধর্মীয় আবহে। আগরবাতি জ্বালিয়ে, গোলাপ পানি ছিটিয়ে ইত্যাদি। তদ্রূপ প্রতিবেশী সমাজের ব্যবসায়ীরাও হালখাতা করেন তাদের নিজস্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে। দোকান বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঠাকুর দেবতার মূর্তি থাকে। গনেশের, লক্ষীর। সেখানে ফুল দেয়া হয়, ধূপ-ধূনো দেয়া হয়, প্রণাম করা হয়। কোথাও কোথাও গঙ্গাজল ছিটানো হয়। কোথাও ঢাকের বাদ্য থাকে, আবার কোথাও কোথাও মাইক বাজে। দোকানদার-ব্যবসায়ীরা আমন্ত্রিতদের মিষ্টিমুখ করান। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এটাই ছিল পহেলা বৈশাখ পালন। আর তা ছিল দোকানদার-ব্যবসায়ী এবং ভোক্তা ও ক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে পশ্চিমবঙ্গের শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ উদযাপনের বন্দোবস্ত করেছিলেন। শান্তি নিকেতনে পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হয়েছে কার্যত একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবেই। বাঙালী সংস্কৃতি বলতে তিনিও যে কার্যত হিন্দু সংস্কৃতিই বুঝাতেন সে প্রমাণ দিয়ে ‘রবী জীবনী’র সপ্তম খণ্ডে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, ‘ওই বৎসর নববর্ষের দিনটি রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে ছিলেন, তাই প্রথানুযায়ী ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে মন্দিরে উপাসনা করে বর্ষবরণ করেন।’ বরণ কথাটা প্রতিবেশী সমপ্রদায়ের ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট।
এরপর উক্ত গ্রন্থের ২৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ষশেষের উপাসনার কথা আছে। প্রশান্ত কুমার পাল লিখেছেন, ‘৩১ চৈত্র (শুক্র, ১৩ এপ্রিল) সন্ধ্যায় কলকাতার বহু অতিথি এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বর্ষশেষের উপাসনা করেন।’ বর্ষবিদায়টাও এখানে তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও মেলা হয় না। কলকাতায়ও নয়। মেলা হয় চড়ক উপলক্ষে। কিন্তু ঢাকার একটা দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয় নিবদ্ধে ১৪১২ সনের গত পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তির কথাও আছে। এ সবই বাঙালী সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু চৈত্র সংক্রান্তি এবং চড়ক সংক্রান্তি তো একই জিনিস। সুবল চন্দ্র মিত্র সংকলিত ‘সরল বাঙালা অভিধানে’ ‘চড়ক’ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে :
‘‘চড়কের দুই দিন পূর্বে ‘কাঁটা ঝাঁপ’ বা ‘আগুন ঝাঁপ’ হইয়া থাকে। চড়কের অব্যবহিত পূর্ব দিবসে উপবাস করিয়া সন্ন্যাসীরা ‘নীল’ (মহাদেবের সহিত লীলাবতীর বিবাহ উৎসব) সম্পন্ন করে। চড়ক পর্ব উপলক্ষে বিশেষত চড়কের দিবস তারকেশ্বরে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়। পূর্বে চড়ক উপলক্ষে ‘বাণ’ ফোঁড়া হইত; ভক্ত সন্ন্যাসী স্বীয় গন্ডদেশ বা জিহবা লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া মহাদেবের প্রীত্যর্থে আপন শরীর নিগ্রহ করিত। পৃষ্ঠদেশ লৌহ বড়শি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহাতে রজ্জু বদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসীরা পাক খাইত। ১৮৬৩ খ্রী. অ. ইংরেজ গভর্ণমেন্ট লৌহশলাকা বা হুকের ব্যবহার বন্ধ করিয়াছেন। অধুনা পৃষ্ঠে দড়ি বাঁধিয়া পাক খাইতে বাধা নাই।’’ তাই না ‘চড়ক’ চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় পর্ব।’
গত ১ বৈশাখ ১৪১২ (১৪ এপ্রিল ২০০৫) তারিখ বৃহস্পতিবার ঢাকার একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় নববর্ষের ওপর লেখা সম্পাদকীয় নিবন্ধে চৈত্র সংক্রান্তিকে গোটা বাঙালী জাতির উৎসব হিসেবে দেখানো হয়েছে। এটা বাংলাভাষী প্রতিবেশী সমাজের মানুষদের পর্ব হিসেবে দেখালে ঠিক আছে। কিন্তু একে বাংলাভাষী মুসলমানদেরও একটি পর্ব হিসেবে দেখানো হলে তা যে সচেতন মুসলমানদের অনেকেরই কাছে আপত্তিকর বিষয় হয়ে ওঠে তা অনেকের প্রতিক্রিয়া থেকেই বোঝা যায়। এ রকমই তাদের প্রতিক্রিয়া যে, লাঙ্গলবন্দের স্নান উৎসবে অংশগ্রহণ করার অধিকার প্রতিবেশী সমাজের আছে। সেটা তারা মানেন ঠিকই, কিন্তু এর সঙ্গে কৌশলে মুসলমানদের জড়ানো কেন? গত ১৬ এপ্রিল ২০০৫ (৩ বৈশাখ ১৪১২) তারিখ শনিবার ঢাকার একটি দৈনিকে ‘লাঙ্গলবন্দ স্নানের অমৃত উৎসব’ শিরোনামে একজনের লেখায় ‘সর্বধর্মের সমন্বয়ে’র আকাঙ্খা ব্যক্ত হয়েছে। এই নিবন্ধেই ভদ্রলোক ইতোপূর্বে কিন্তু লিখেছেন, ‘তীর্থস্থান সকল হিন্দুর সাধনার ফল।’ কিন্তু যা ‘হিন্দু সাধনার ফল’ এবং হিন্দুর ‘তীর্থস্থান’ সেখানে মুসলমানদের জড়ানো কেন? এ রকম একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে সংখ্যাগুরুর ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতিকে সংখ্যালঘুর ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয়ের আহ্বান কেন?
মুসলমানরা সমন্বয় নয়, বিভিন্ন ধর্মীয় সমপ্রদায়ের মানুষের মধ্যে আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সহাবস্থান চান। আমাদের প্রতিবেশী সমাজের সমাজপতিরা এতে সন্তুষ্ট নন কেন? তারা সহাবস্থানের কথা না বলে সমন্বয়ের কথা কেন বলেন? এর কারণ এই যে, বৈদিক ব্রাহ্মণ-শাসিত মনুসংহিতার সমাজ ছাড়া আর কোনো সমাজের অস্তিত্ব তারা এই উপমহাদেশে মানতে চান না। উপমহাদেশে মুসলমানদের কোনো ধরনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অসি-ত্বেরও তারা বিরোধী। তাদের আকাঙ্খা এই যে, উপমহাদেশে মুসলমানদেরকে তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতি ত্যাগ করে বৈদিক ব্রাহ্মণ শাসিত মনুসংহিতার সমাজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে। এরপরও তারা ন্যূনতম নাগরিক অধিকার দাবী করতে পারবেন না। এই কথাগুলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (আর.এস.এস-এর) তাত্ত্বিক নেতা গুরু গোলওয়ালকর তার ‘উই আর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইল্ড’ শীর্ষক পুস্তিকায় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় খোলাখুলিই বলেছেন। এটা ঠিক যে, প্রতিবেশী সমাজে সহাবস্থানকামী এবং মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন অনেক গুণীজন আছেন। কিন্তু পাশাপাশি এও একটি কঠিন বাস্তবতা যে, বৈদিক ব্রাহ্মণ শাসিত মনুসংহিতার সমাজের কোনো শাসক দল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ এবং তার সাংস্কৃতিক শাখা সংগঠন বজরং দল এবং হিন্দু পরিষদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি। শিক্ষাঙ্গনে আরএসএস-এর শাখা সংগঠন বিদ্যার্থী পরিষদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। আরএসএস-এর দুর্গা বাহিনী এবং অন্যান্য শাখা সংগঠনও নিষিদ্ধ নয়। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর শিবসেনা প্রধান বাল থ্যাকারের নির্দেশে বোম্বাইয়ে মুসলিম হত্যাযজ্ঞ চালানো হলেও শিবসেনাকে কোনো সরকারই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি। বোম্বাইয়ের মুসলিম হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের রিপোর্টও আজ পর্যন্ত প্রকাশ করেনি। বস্তুত মনুষ্যত্ববোধে উত্তীর্ণ সহাবস্থানকামী এবং সামাজিক সুবিচারকামীদের সংখ্যা নগণ্য বলেই বাস্তবে এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব। আড়াই হাজার বছর আগে প্রণীত মনুসংহিতায় আছে, ব্রাহ্মণের জন্ম প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়ের জন্ম প্রজাপতি ব্রহ্মার বাহু থেকে, বৈশ্যের জন্ম প্রজাপতি ব্রহ্মার উরু থেকে আর শূদ্রের জন্ম প্রজাপতি ব্রহ্মার পদদ্বয় থেকে। আরএসএস-এর বক্তব্য, উপমহাদেশে থাকবে বৈদিক ব্রাহ্মণশাসিত মনুসংহিতার সমাজ। যদিও শূদ্রেরা গ্রামের বাইরে থাকবে এবং ভাঙা হাঁড়িতে খাবে। উচ্চ বর্ণের লোকেরা তাদের জান, মাল, ইজ্জত ইত্যাদি সবকিছু লুটপাট করলেও তাতে কোনো পাপ হবে না। কেননা পূর্বজন্মের পাপের জন্য এ সবকিছুই তো তারা পরজন্মে ভাল থাকার আশায় ভোগ করতে পারবে। মনুসংহিতার সমাজের সমস্যা হল, শূদ্রের জন্ম যদি প্রজাপতি ব্রহ্মার পা থেকে হয় তাহলে অহিন্দুদের ঠাঁই কোথায় হবে? বিশেষত মুসলমানদের ঠাঁই? এর জবাব হল ঠাঁই যদি দিতে হয় তাহলে তো তাদের ঠাঁই দিতে হয় শূদ্রের পরে অর্থাৎ পায়ের নীচে! তাহলে এর আগে তো মুসলমানদের তাদের ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে, তাদের নিজস্ব জাতিসত্ত্বা থেকে সরিয়ে আনতে হয়। ভারতে তাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের কর্মসূচীর মধ্যে আছে মুসলিম পারিবারিক আইন উচ্ছেদের কথা অর্থাৎ কোরাআন এবং সুন্নাহ থেকে সরিয়ে আনার কথা। সেই পাকিস্তান আমল থেকে মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে বাঙালী সংস্কৃতিকে। মূল পরিকল্পনাটা অবশ্য পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ারও অনেক আগের। আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের ‘দেশ’ পত্রিকা ‘কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা (১৮৮৫-১৯৮৫)’য় প্যাটেলপন্থী প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ ‘ভারত বিভাগ (কার্য ও কারণ)’ শীর্ষক নিবন্ধে ১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ‘শিক্ষিত অধ্যাপকদের দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির চেষ্টা ভারতবিভাগের অন্যতম কারণ। ... হিন্দু অধ্যাপকদের এই অমার্জনীয় মনোভাব শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এইভাবে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এই পার্থক্য সৃষ্টিতে হিন্দুদের অবদান কম নয়। আমার বক্তব্য হয়তো অনেকের মনঃপূত হবে না, কিন্তু এটাই সত্য, কঠোর ও কঠিন সত্য।’
উক্ত নিবন্ধে ১২৫ পৃষ্ঠায় অতুল্য ঘোষ লিখেছেন, ‘সাধারণত পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলের লোকেরা ভারত বিভাগের জন্য গান্ধীজী ও কংগ্রেসকে দায়ী করেন। কংগ্রেসের দায়িত্ব অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু কংগ্রেস ভারতবিভাগে সম্মতি দেয়ার ঢের আগে ১৯৪০-৪১ সালে যখন রাশিয়া বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করল সেই সময়ে সিপিআই (তখন অবিভক্ত সিপিআই) বোম্বাই থেকে প্রকাশিত তাদের ‘পিপলস ওয়র’ কাগজে ভারতবিভাগ যে হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাদের অভিমত প্রকাশ করেন এবং ভারতবর্ষের কোন অংশ কোথায় যাবে তাও এঁকে দেন। ঐ ম্যাপে ভারতবিভাগের ফলে যে যে অঞ্চল নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি অঞ্চল নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠনের সুপারিশ কম্যুনিষ্টরা করেছিলেন। সমস্ত নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলগুলোর পাকিস্তানভুক্তির সপক্ষে মত প্রকাশ করা হয়েছিল। এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। এ প্রসঙ্গে সমাজতন্ত্রী নেতা রাম মনোহর লোহিয়ার উক্তি, ‘দেশবিভাগের ব্যাপারে কমিউনিষ্ট সমর্থন পাকিস্তানের জন্ম দেয়নি। তা কেবল কাজ করেছে ইনকোটরের অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফোঁটানোর যন্ত্র বিশেষের।’’ ঢাকায় প্রকাশিত স্মৃতিকথা ‘ফেলে আসা দিনগুলো’র ৫৫ পৃষ্ঠায় ইব্রাহিম হোসেন লিখেছেন, ‘কমিউনিষ্ট রাজনীতি ছিল আমার কাছে রীতিমত রহস্যময় ব্যাপার। অনেকেই জানে না যে, এরা পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করত। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী, রণেশ দাশগুপ্তের মতো প্রথিতযশা কমিউনিষ্ট নেতা সেকালে পাকিস্তান আন্দোলনকে রীতিমত নিপীড়িত মানুষের আন্দোলন বলে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছেন। অথচ পাকিস্তান হওয়ার পর এঁরাই আবার বলতে শুরু করছেন, এটা নাকি একটা ধর্মান্ধ সামপ্রদায়িক দেশ এবং তা হচ্ছে সর্বপ্রকার প্রগতিবিরোধী একটা মধ্যযুগীয় কান্ডকারখানা।’ লক্ষণীয় যে, পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাপারে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সাতচল্লিশ পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গির সংগে সাতচল্লিশ পরবর্তী কথার মিল নেই। একটা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জন্ম তারাই দিয়েছিলেন। ইব্রাহিম হোসেন সাহেব তার পূর্বোক্ত স্মৃতিকথা ‘ফেলে আসা দিনগুলো’র ৫২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ‘ভাষা আন্দোলনকারীদের সাথে কমিউনিষ্ট পার্টি ও কংগ্রেসের একটা যোগাযোগ ছিল। কিন্তু সেটা কখনো প্রকাশ্য ব্যাপার হতে পারেনি। আমি নিজে লক্ষ্য করেছি, ভাষা আন্দোলনকারীদের মিছিল-মিটিং চলাকালে কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস ও লাইব্রেরীগুলো বিশেষ তৎপর হয়ে উঠত। কংগ্রেসী নেতাদের মনে হত খুব কর্মচঞ্চল। ভাষা আন্দোলনকারীদের লিফলেট-ইশতেহার ও অন্যান্য প্রচারপত্র তারা নিজেরা অনেক সময় স্বেচ্ছায় বিলি-বাটোয়ারা করে দিত।’’
অবিভক্ত ভারতে বাংলায় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন মুসলিম। তখন তাদের লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্যপীড়িত গণমানুষের কথা চিন্তা করে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা। অবিভক্ত বাংলায় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন মোট চারজন। এই চারজনই ছিলেন মুসলমান। এঁরা হলেন, মুজফফর আহমদ, আবদুর রাজ্জাক খাঁ, আবদুল হালিম এবং সামসুল হুদা। (শেখ দরবার আলম ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ এপ্রিল, ২০০৫) পরে যুগান্তর ও অনুশীলন দল থেকে এসে অনেকেই যোগ দিলেন কমিউনিষ্ট পার্টিতে। কংগ্রেসের সন্ত্রাসবাদী এই সংগঠন দুটো থেকে আসা কমিউনিষ্ট পার্টির এইসব টেরো কমিউনিষ্ট এবং টেরো সোশ্যালিষ্টদের নজর পড়ল কালক্রমে মুসলমানদের ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতি বদলে দেওয়ার দিকে। কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফোঁটানোর মতো বাংলাভাষী মুসলমানদের ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতি বদলে দেওয়ার মূল কর্মসূচি হিসেবে তারা আনলেন বাঙালী জাতীয়বাদ এবং বাঙালী সংস্কৃতির কথা। ধর্মভিত্তিক হোক, ভাষাভিত্তিক হোক, কিংবা অঞ্চলভিত্তিক হোক, যে কোনো নামে শোষণ ও বঞ্চনার সংস্থান সৃষ্টির জন্য সামপ্রদায়িকতার জন্য ইতিহাস বিকৃতির প্রয়োজন হয়। ঠিক এই নিরিখেই কিছু সংগঠন এবং সংস্থা পহেলা বৈশাখ উদযাপন করে আসছে। নানান জীবজন' এবং মুখোশকে তারা বাঙালী সংস্কৃতি বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। বাঙালী সংস্কৃতির নামে তারা ‘প্রকৃতি দানব নিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা’ বের করেছে। বাঙালী সংস্কৃতির নামে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে মঙ্গল প্রদীপ, আলপনা। তৌহীদে বিশ্বাসী মুসলমানদের তারা ভাষ্কর্যের নামে অভ্যস্ত করতে চাচ্ছে পৌত্তলিকতায়। সেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে পাকিস্তান আমলেও কেবল প্রতিবেশী সমাজের লেখা তাদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতিপ্রধান সাহিত্যকেই আমরা এমনভাবে আমাদের সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ করেছি যে, মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতিকে আমরা সামপ্রদায়িক বলে ভাবতে শিখেছি, সামপ্রদায়িকতার অর্থটুকু পর্যন্ত না বুঝেই।
ভারত সম্রাট আকবরের আমলে তাঁরই নির্দেশে হিজরী সনের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত ও প্রবর্তিত ফসলী সন বাংলা সনের প্রবর্তন। হিজরী সনের ওপর ভিত্তি করে খাজনা আদায়ে সুবিধার্থে এই ফসলী সনের পঞ্জিকা প্রণয়নও তো করেছিলেন পন্ডিত আমীর ফতেহ উল্লাহ সিরাজী, যিনি ছিলেন একজন মুসলমান। যে সনের পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন মুসলমান, যে সন প্রবর্তন করেন মুসলমান, সেই সনের পহেলা তারিখ উদযাপন উপলক্ষেও আমাদের মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলছে। এর থেকে বড় ইতিহাস বিকৃতি আর কী হতে পারে? আমাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তাই এদেশে মুসলমানরা নিজ ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতির অনুসরণে সুস্থ জীবনবোধে স্থিত থাকার পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্র এবং সরকারের। দেশের অন্যান্য সমপ্রদায়ের সংগে ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতির পরম্পরা সংরক্ষণের দায়িত্ব সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপর।
বাংলাদেশে যে সকল সংগঠন, সংস্থা, সংবাদপত্র এবং মিডিয়া সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ইসলামী সংস্কৃতি উৎখাত করে হিন্দু-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে তারা কোন্ অধিকারে গণমুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানছে? এ সমস্ত কর্মকান্ড সরকারের অবশ্যই নিষিদ্ধ করা উচিত। কোন হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি হিসাবে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করতে চাইলে তা তাদের মন্দিরে করতে হবে। যেমন রবীন্দ্রনাথ করতেন শান্তি নিকেতনে মন্দিরের নববর্ষের উপাসনা করে।
তিন.
দুনিয়াব্যাপী আজ মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগ। পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য হল, সে যদি বিষ্ঠার উপরেও টাকা দেখে, তা তুলে নেবে। মুনাফার জন্য আজ মানুষ সব কিছু করতে পারে। তাই মার্টিন লুথার কিং বলেছেন, ধষসরমযঃু ফড়ষষধৎ!! প্রতিবেশী বিশাল ভারতের ‘রাজভাষা’ হিন্দি। আর ভারতের বাজার ১০০ কোটি মানুষের বাজার। মুক্তবাজার অর্থনীতির দানব আমাদের কাউকেই মানবে না, কোনো হিতোপদেশে গলবে না, সে ফুলবনে মত্তহস্তীর মতা সব বাগানগুলোকে লন্ডভন্ড করে দেবে! আগে কলকাতায় প্রশ্ন হত, আপনি বাঙালী না মুসলমান? যেন মুসলমানরা বাঙালী হয় না!! কিন্তু মুক্তবাজারের আর্শীবাদে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দির দাপটে বাঙালীর অবস্থা এমনই শোচনীয় যে, এখন প্রশ্ন হয়, আপনি বাঙালী না হিন্দু? যেন হিন্দুরা বাঙালী হয় না!!
কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল, রাণিগঞ্জ প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে বাঙালী ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘু হয়ে গেছে। সেখানে রাজভাষায় নিমজ্জিত মগজধোলাইপ্রাপ্ত অধিকাংশ বাঙালী আজ দাসে পরিণত হয়ে গেছে, অবশিষ্টরা ‘প্রাদেশিক’ আখ্যায় ভূষিত হওয়ার ভয়ে নীরবতার ব্রত গ্রহণ করেছে। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা মাঝে মধ্যে বাংলাভাষার সম্মানার্থে হুংকার ছাড়েন ঠিকই কিন্তু বিশ্বায়নের নামে যে দূষণ নিরন্তর চলছে সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। বাংলাদেশও এখন মুক্তবাজার অর্থনীতির দ্বার খুলে দিয়েছে। টাকার কাছে সবই তুচ্ছ, ফুলের গুচ্ছ তো বটেই, এমনকি সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যও। ফলে যে কোন বহুজাতিক কোম্পানী এই উপমহাদেশের জন্য কোনো কিছু বাজারজাত করতে চাইলে প্রথমে তা করে ওই ১০০ কোটির বাজার লক্ষ্য করে। হিন্দি ভাষা ও হিন্দি সংস্কৃতিই হয় তার আহ্বান। সেটারই একটা যেনতেন বাংলা সংস্করণ পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশে। তাতে যদি তাদের ব্যবসা হয়, শুধু রুচির কথা বলে, সংস্কৃতির দোহাই পেরে কি তাকে থামানো যাবে? তাই ঢাকার হাটবাজারে অচিরেই হিন্দিতে কথা বলতে হবে নাকি? দেবনাগরিকে বাহন করে উর্দূ কি আবার আসছে বাংলাদেশে?