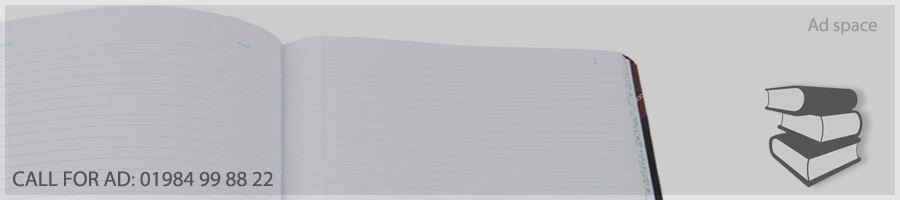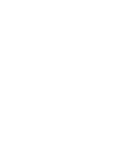শাস্তিদানে মাত্রাজ্ঞান
সে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ ও স্নেহভাজন। কোলে-পিঠে থাকার বয়সে আমার সাথে বেশ সখ্য ছিল। আমার বুকের ’পরে তার পেলবমধুর ঘুম অনেক উপভোগ করেছি। সেই কারণেই কিনা ঠিক জানি না, ওর প্রতি কোনও অপ্রীতিকর আপতন আমার বুকের ভেতর বেশ বাজে। সদ্য বেজে ওঠা সেরকম এক বেদনাই এবারকার লেখার উদ্দীপক।
খবর আসল শিশুটিকে পাওয়া যাচ্ছে না। এক আবাসিক প্রতিষ্ঠানে পড়ত। সেখান থেকে কখন বের হয়েছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না। এ রকম সংবাদে বাবা-মায়ের উপর দিয়ে কী কেয়ামত ঘটে যায় তা অনুভূতিসম্পন্ন যে-কেউ কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারে।
অনেক খোঁজাখুজি করা হল, আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ হল এবং ওর বাবা-মাকে দু’কথা সান্ত্বনা দেওয়ারও চেষ্টা করা হল। আল্লাহ তাআলার মেহেরবাণী যে, সেই কিয়ামত প্রলম্বিত হয়নি। জানা গেল সে তার নানাবাড়ির পথ ধরেছে। নিঃসন্দেহে একটি শিশুর পক্ষে এতটা দূরের সফর অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। আল্লাহ তাআলার শুকর- তিনি নিরাপদেই তাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছেন।
না বলে-কয়ে কেন এভাবে চলে গেল? কিংবা বলুন, পালাল কেন? না এটা স্কুল পালানোর কোনও সৌখিন ও আমুদে এ্যাডভেঞ্চার নয়। বরং ছিল আতঙ্কিত পলায়ন। মারধর আর সইতে পারছিল না। পরের দিন তার পরীক্ষা ছিল। ভালো না পারলে কপালে দুঃখ আছে এবং সে দুঃখ যে নির্মম বেত্রাঘাতরূপেই দেখা দেবে সে অভিজ্ঞতা তার ইতোমধ্যে হয়ে গিয়েছিল। ও কচিদেহ সে মার কিছুতেই বইতে পারবে না, এটা জানা ছিল। অগত্যা পলায়নেই মুক্তি। সিদ্ধান্ত যে বেঠিক নেয়নি পিঠের কাপড় সরাতেই তার সাক্ষাত প্রমাণ মিলল। সারা পিঠে কালশিরা দাগ।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র পালানোর ঘটনা আমরা হামেশাই শুনে থাকি। এ রকম শত-শত ঘটনা আমাদের স্কুল-মাদরাসাগুলোর ইতিহাসে আছে। অধিকাংশ ঘটনাই ঘটে কোনও না কোনও নির্যাতনের কারণে। সে নির্যাতন শাস্তিদানের প্রক্রিয়ায় হোক কিংবা শিক্ষাদানের ধারায়। ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষাও এক সাক্ষাৎ নির্যাতন। সে আলোচনা পরে কখনও। এক্ষণে আমাদের নজর শাস্তিদানের প্রতি।
শিক্ষার সাথে শাস্তিদানের এক অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক আছে। আবহমানকাল থেকেই এটা চলে আাসছে। এ সম্পর্ক এতই নিবিড় যে, অনেক সময় শিক্ষাকে শাস্তির প্রতিশব্দ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বলা হয়, তাকে ‘উচিত শিক্ষা দিতে হবে’, মানে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। আরবীতেও تأديب শব্দটি শিক্ষাদান ও শাস্তিদান উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এটা সম্ভবত এ কারণে যে, শিক্ষাদান করতে গেলে শাস্তিদানেরও প্রয়োজন হয়, তা যে পর্যায়েরই শাস্তি হোক না কেন। কাউকে কোনো বিষয় শেখানো হয়েছে, অথচ তাকে কখনও কোনও রকমেরই শাস্তি দিতে হয়নি, এমন কদাচ ঘটে। এর দ্বারা বোঝা যায়, শিক্ষার জন্য শাস্তিদানের প্রয়োজন এক অনঃস্বীকার্য বাস্তবতা। কেউ অস্বীকার করলে তা তার বাড়াবাড়ি।
তবে শাস্তিদানের কাজটি খুব সহজ নয়। এর জন্য গভীর বিচার-বিবেচনা দরকার। স্থান-কাল-পাত্র-মাত্রা ইত্যাদির দিকে নজর রাখা অত্যন্ত জরুরি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা রাখা হয় না। ফলে শাস্তি প্রয়োগে চরম বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। বাড়াবাড়িমূলক শাস্তি কখনও সুফল বয়ে আনে না। কার্যত সুফল পাওয়াও যাচ্ছে না। এটা বেমক্কা শাস্তিরই কুফল যে, শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকছে। অনুপস্থিত থাকার জন্য অজুহাত তৈরি করছে, তা কাজে না লাগলে পলায়ন করছে এবং একপর্যায়ে তার শিক্ষাজীবন ঝড়ে যাচ্ছে। কেবল মাত্রাতিরিক্ত শাস্তির কারণেই কত শিক্ষার্থী মাঝপথে বা সূচনাপর্বেই হারিয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। তাঁদের এই ব্যর্থতার দায় কার?
অতিরিক্ত শাস্তির নির্যাতন সয়েও যেসব শিক্ষার্থী শেষ পর্যন্ত থেকে যায়, তারাও কি কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়? শাস্তির আতংক ব্যক্তিগঠনের পক্ষে এক কঠিন বাধা। এটা পড়াশোনার গতিবেগকে ব্যহত করে। এর ফলে শিক্ষার্থীর মানবিক বিকাশ বিঘ্নিত হয় এবং তার অসাধু প্রবৃত্তি প্ররোচিত হয়। তাছাড়া এটা স্বাস্থ্যহানিরও কারণ। সুতরাং যারা উতরে যায় তারাও এতসব ক্ষতির শিকার হয়েই উতরোয়। যে ছেলেটা আরও কম সময়ে হাফেয হতে পারত দমন-পীড়নজনিত নির্জীবতার কারণে তা হতে পারেনি। সময় বেশি লেগে গেছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মেয়াদে যে শিক্ষার্থী বিস্তর পড়াশোনা করতে পারত, তা সে করতে পারেনি। ভয়-ভীতিজনিত অবদমন তাকে তা করতে দেয়নি। যুতটুকু পুঁজিও সে তার এই মেয়াদে আহরণ করতে পেরেছে, তাও মানসিক বিকাশের অভাবে কর্মজীবনে যথেষ্ট সুফলদায়ী হয় না। তার চরিত্রে সংযম, হিম্মত, সততা, উদারতা প্রভৃতি সদগুণের উৎকর্ষ সাধিত হতে পারেনি। উল্টো সে হয়ে পড়েছে একধরণের মনোবৈকল্যের শিকার। তাই অধীত বিদ্যার উপযুক্ত প্রয়োগ তার পক্ষে সম্ভব হয় না। গতানুগতিক নির্জীব খাটুনিই হয় তার জীবনের সার। ব্যক্তিগঠন ও সমাজ নির্মাণে তা বিশেষ ভ‚মিকা রাখতে পারে না। আমভাবে এ দৃশ্যই তো সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থার পরিবর্তন জরুরি।
প্রথমেই চিন্তা করা দরকার শাস্তিদানের উদ্দেশ্য কী? সে দিকে নজর না রেখে শাস্তি দিলে তাতে কেবল মনের ঝাল মেটানোই হয়, কাজের কাজ কিছু হয় না। উদ্দেশ্য যদি হয় তরবিয়ত ও ব্যক্তিগঠন তবে শাস্তিদানের আগেও অনেক কিছু করণীয় আছে। কঠোরপন্থা অবলম্বনের আগে নম্রকোমল আচরণ কর্তব্য। তারও আগে দরকার পাত্রপাঠ। অর্থাৎ উপযুক্ত করে যাকে গড়ে তোলা লক্ষ, তার স্বাস্থ্য, মেধা, রুচি-মেজাজ ও পারিপার্শ্বিক সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে আপাত বিচারে তার পক্ষে কতদূর পৌঁছা সম্ভব তা নিরূপণ করে নিতে হবে। সব শিক্ষার্থী সমমানের হয় না। বিভিন্ন দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকেই। উস্তায ও অভিভাবকের তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়।
অন্ততপক্ষে তিনটি ক্ষেত্রে এই পার্থক্য মাথায় রাখা দরকার। (ক) পাঠদান ও শিক্ষা-দীক্ষা বিষয়ক অন্যান্য কাজ আদায়ের ক্ষেত্রে; (খ) তার সার্বিক পরিচর্যা ও প্রযত্নের ক্ষেত্রে; (গ) প্রত্যাশিত ফলাফল লাভের ক্ষেত্রে।
পাঠদান ও অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অবস্থাগত পার্থক্যের প্রতি লক্ষ রাখলে তাদের কারও প্রতি সাধ্যাতীত ভার চাপানো হবে না। বহনযোগ্য হওয়ার কারণে পাঠ্যবিষয় আয়ত্তকরণ ও অন্যান্য কর্তব্যকর্ম পালনে প্রত্যেকেই সাধ্যমত উৎসাহী থাকবে। জানা কথা- সোৎসাহে কৃত কাজে অগ্রগতি সন্তোষজনক হয়। ফলে শাস্তিদানের প্রয়োজন কমে আসে।
শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলাই যখন উদ্দেশ্য থাকে, তখন পাঠদান ও কাজ দেওয়াতেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তার পরিচর্যাও জরুরি। অর্থাৎ কর্তব্যকর্ম সে ঠিকভাবে পালন করছে কি না, না করে থাকলে কেন করছে না, তার সমস্যা কোথায়, সমস্যা কি শাস্ত্রগত না স্বাস্থ্যগত, না চারিত্রিক, না কি পারিবারিক। এসব বিষয় খতিয়ে দেখাও একজন আদর্শ শিক্ষক ও অভিভাবকের অবশ্যকর্তব্য। সমস্যা শনাক্ত করার পর তা নিরসনের জন্য উপযুক্ত ও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জায়গা মত দাওয়াই দিতে পারলে তাকে কর্তব্যকর্মে মনোযোগী করে তোলা অবশ্যই সম্ভব। সারকথা দায়িত্বশীলতার সাথে যদি শিক্ষার্থীর পাশে থাকা যায়, তবে শাস্তিদানের অবকাশ অনেক হ্রাস পাবে।
অতপর প্রত্যাশিত ফলাফলেও যদি ছাত্রদের অবস্থাগত পার্থক্যকে বিবেচনায় রাখা হয়, তবে সহসাই মেযাজ খারাপ হবে না। ফলাফল বলতে কেবল পরীক্ষার ফলাফলই বোঝায় না। সেই সাথে দৈনন্দিন পাঠ ও অন্যান্য কর্মসূচী পালনের মান ও পরিমাণও বিবেচ্য। উন্নতির ধারাবাহিকতাও ফলাফলের মধ্যে পড়ে বৈকি! মেধা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্যহেতু সঠিক ফলাফলে প্রভেদ ঘটতে বাধ্য। কাজেই চেষ্টার ত্রুটি যদি না থাকে, আর কেবল মেধার দুর্বলতা বা অলঙ্ঘনীয় পারিপার্শ্বিকতার কারণে শিক্ষার্থী যদি আমার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ফললাভ না করে, তবে সেজন্য তাকে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য মনে করার কোনও অবকাশ নেই। এ সত্য বিস্মৃত হওয়ায় অনেক ছাত্রকেই শিক্ষক বা অভিভাবকের হাতে নিগৃহীত হতে হয়। এটা খুবই দুঃখজনক। মনে রাখতে হবে, ছাত্রের কাছে আমার প্রত্যাশা আমার নিজ স্বপ্ন অনুযায়ী নয়; বরং ছাত্রের মেধা ও প্রতিভা অনুযায়ী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।
উপরিউক্ত তিনও ধাপেই শিক্ষক ও অভিভাবককে কঠোরতার উপর কোমলতাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। শাস্তি ও কঠোরতা হবে শেষ অস্ত্র। যতক্ষণ কোমলতায় কাজ হয় ততক্ষণ সে অস্ত্র পরখের বৈধতা থাকে না। শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যেজন। এটাই প্রাকৃতিক ধর্ম। আল্লাহ তাআলারও শান হল, سبقت رحمتي غضبي ‘আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর অগ্রগামী থাকে।’ দয়া ও মমতার আচরণ কর্মীকে কাজে উদ্দীপিত করে। তার মনে অনুপ্রেরণা যোগায়। ফলে সে কাজ করে স্বতঃস্ফ‚র্তভাবে ও আন্তরিকতার সাথে। এ অবস্থায় কাজ হয় সুচারূ ও নিখুঁত, যেমনটা প্রত্যাশা থাকে। কাজেই প্রত্যাশিত ফল পেতে হলে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীকে স্ফ‚র্তির ভেতর রাখা আবশ্যক। ভুল তার দ্বারা হতেই পারে। সেক্ষেত্রে নম্রতার সাথে বোঝাতে হবে। দরদী ভাষা ব্যবহার করতে হবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় আমরা দরদী আচরণেরই প্রাবল্য দেখি। হাদীস শরীফে তাঁর শিক্ষাদান সম্পর্কিত কোমলমধুর আচরণের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। একটা ঘটনা উল্লেখ করা যাক-
‘একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামসহ মসজিদে উপবিষ্ট। এ অবস্থায় এক বেদুঈন এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করল। তারপর সে মসজিদের এক পাশে গিয়ে প্রশ্রাব করতে শুরু করল। সাহাবায়ে কিরাম তার দিকে তেড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি তাদের বারণ করলেন। যখন তার প্রশ্রাব করা শেষ হল, তিনি তাকে কাছে ডাকলে। বললেন, দেখ, এ মসজিদ এমন স্থান নয়, যেখানে প্রশ্রাব করা যাবে। বরং এটা নির্মিত হয়েছে নামায পড়ার জন্য, যিকর ও তাসবীহের জন্য এবং কুরআন তিলাওয়াতের জন্য। তারপর তিনি সাহাবায়ে কিরামকে আদেশ করলেন, বালতিতে পানি এনে ওখানে ঢেলে দাও। (তার এ স্নেহপূর্ণ আচরণে বেদুঈন মুগ্ধ হয়ে যায়)। অনন্তর সে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে বলল, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক। পরে সে বলত, তিনি আমাকে একটু তিরস্কারও করলেন না, একটু গালিও দিলেন না। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২২০; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৫৬
এ হাদীস থেকে আমরা কতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করেছি? অর্ধেক করেছি। তা হচ্ছে, মাটিতে প্রশ্রাব বা অন্য কোনও তরল নাপাকি পড়লে তা পবিত্র করার উপায় কী? এ হাদীস দ্বারা তার সমাধান নেওয়া হয় এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনাও হয়। কিন্তু ওখানেই ক্ষান্ত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। এর ভেতর যে আখলাকী সবক আছে এবং আছে শিক্ষাদানের নীতি সম্পর্কে নির্দেশনা তাও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা উচিত। কোমল পন্থায় শিক্ষাদান করলে তার কী সুফল পাওয়া যায়, তাও আমরা হাদীসের এ ঘটনায় দেখতে পাচ্ছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখেরী নবী। কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্য তিনি মানব জীবনের প্রাসঙ্গিক যাবতীয় বিষয়ের শিক্ষাদাতা। তাঁর শেখানো পদ্ধতি তখন যেমন প্রযোজ্য ছিল আজও তেমনি প্রযোজ্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত সমান প্রযোজ্য থাকবে। শোনা যায় শিক্ষাদানের এই কোমল ও সহনশীল পন্থা অমুসলিম কোনও কোনও দেশে অনুসৃত হচ্ছে, কিন্তু আফসোস, আমরা মুসলিম হওয়া সত্তে¡ও আমাদের নবীর নির্দেশনা অনুসরণ করছি না। আমাদের দেশের স্কুল-মাদরাসাগুলো আজও পর্যন্ত এ আদর্শ রপ্ত করতে পারল না। পত্র-পত্রিকায় মাঝে-মধ্যেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি যে নির্দয় আচরণ করা হয়, তার সচিত্র প্রতিবেদন চোখে পড়ে এবং তা রীতিমত লোমহর্ষক। (প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস আমাদের অন্তরে আলো জ্বালুক- আমীন)।
আমরা এমন দাবি করতে পারি না যে, আদর-সোহাগ দ্বারাই ষোল আনা সুফল পাওয়া যাবে। কেননা শয়তানের প্ররোচনা, পরিবেশ-পরিস্থিতির উস্কানি ও প্রবৃত্তির তাড়না তো আছেই। ব্যক্তিগঠনমূলক যে কোনও প্রচেষ্টাই ক্ষেত্র বিশেষে এর দ্বারা ব্যাহত হতে পারে। সেক্ষেত্রে কঠোরতা প্রাসঙ্গিক বৈকি! কিন্তু তার প্রয়োজন যে খুব বেশি থাকবে না এটা নিশ্চিত। মাঝে-মাঝে হয়ত দরকার হবে, কিন্তু তা পরিবেশের মাধুর্যকে ক্ষুণœ করবে না, যদি শাস্তিদানের শর্তসমূহ পূরণ করা হয়।
প্রকাশ থাকে যে, শাস্তিদান বলতে কেবল বেত্রাঘাতকেই বোঝায় না। স্থান-কাল-পাত্রভেদে তা বিভিন্নরকম হতে পারে। শাস্তি যেমন দৈহিক হতে পারে, তেমনি হতে পারে মানসিক। কারও সংশোধনের জন্য একটু চোখ-রাঙানিই যথেষ্ট হয় আবার কারও জন্য দরকার হয় শারীরিক পীড়ন। কখন কার জন্য কোনটা প্রয়োজন তা বিবেচনায় না রাখলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী শুরুটা হওয়া হওয়া দরকার লঘু শাস্তি দ্বারাই। বোঝানোতে কাজ না হলে চোখ-রাঙানি কি ধমক প্রাথমিক ব্যবস্থা হতে পারে। তারপর তিরস্কারও ভালো ওষুধ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কখনও এটা ব্যবহার করেছেন। তবে এমন কোনও পরিবেশে তিরস্কার করা ঠিক নয়, যা তিরস্কৃতের পক্ষে অপমানকর হতে পারে। উদ্দেশ্য তো অপমান করা নয়? বরং তাকে শোধরানো ও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অপমানকর ব্যবস্থা দ্বারা সে উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। উল্টো তা হীনম্মন্যতা সৃষ্টি করে ও ক্ষোভ জন্মায়। যা ব্যক্তিগঠনের পক্ষে কঠিন অন্তরায়। একই কারণে কানে ধরানোর শাস্তিও প্রযোজ্য নয়। কেননা এটা মারাত্মক অপমানকর। অনেকে এ শাস্তি দিয়ে মজা পায় এবং এর জন্য বিচিত্র পন্থা অবলম্বন করে, যেমন কানে ধরে ওঠানামা করানো, কানে ধরে মুরগি বানানো, একজনকে দিয়ে আরেকজনের কান ধরানো ইত্যাদি। এ ধরনের বিকৃত আনন্দচর্চা অন্তত শিক্ষকের পক্ষে কিছুতেই শোভনীয় নয়। এর দ্বারা শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। তার মানসিকতা ধ্বংস হয়।
কাউকে শোধরানোর একটা উত্তম ব্যবস্থা হল কথা বন্ধ করে দেওয়া। ‘তুমি এমন করেছ? যাও তোমার সাথে কথা বলব না’। অনুচিত শাস্তিভোগে যার হৃদয়-মন নষ্ট ভ্রষ্ট হয়নি, কথা বন্ধের শাস্তি তাকে নাড়া দেবেই। বিশেষত এ ব্যবস্থা যদি হয় এমন শিক্ষকের পক্ষ থেকে, যার আন্তরিকতা ও স্নেহ-মমতায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণ আপ্লুত হয়ে আছে। অন্যায়-অপরাধ শোধরানোর এটা এক সনাতন পদ্ধতি। আমরা শৈশবে পাঠ্যপুস্তকে ‘আনোয়ার আমচোর’-এর ঘটনা পড়েছিলাম। তাতে কথাবন্ধের শাস্তি কি চমৎকারভাবেই না নিজ কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে। সহপাঠী ও বন্ধুদের সাথে কথা বলার জন্য ব্যাকুল-কাতর আনোয়ার শেষাবধি আর চুরি না করার শপথ নিতে বাধ্য হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরামের জীবনচরিতেও এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, যাতে তাঁরা অন্যায়াচরণকারীকে শোধরানোর জন্য কথাবন্ধের শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। কারও উপরে খোদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃকও এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তাবূকের যুদ্ধ যোগদানের ব্যাপারে যে তিন সাহাবীর দ্বারা গড়িমসি হয়ে গিয়েছিল, তাদের প্রতি তিনি এ শাস্তিই আরোপ করেছিলেন। তাদের উপর এটা পরশমণির কাজ করেছিল। কুরআন মাজীদের হৃদয়গ্রাহী শৈলীতে তাদের সে কাহিনী বিবৃত হয়েছে। আজ কুরআন মাজীদে হযরত কা‘ব ইবনে মালিক রা., হযরত মুররা ইবনুর রবী রা. ও হযরত হিলাল ইবনে উমায়্যা রা.-এর ঘটনা যখন পাঠ করা হয়, তখন কোনও দোষী অপরাধীর নয়; পরশমণির ঘর্ষণে খাঁটি সোনায় পরিণত মহান তিন আদর্শপুরুষের ছবিই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে।
যা হোক ব্যক্তিগঠনের পরে কথাবন্ধের শাস্তি একটি প্রয়োগযোগ্য ও ফলপ্রসু ব্যবস্থা। তবে এ ব্যাপারেও সতর্কতার দরকার আছে। সবকিছুই সীমার মধ্যে রাখা বাঞ্ছনীয়। কথাবন্ধের পর সতর্ক পর্যবেক্ষণ জরুরি। কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা লক্ষ রাখা চাই। বেশি কষাতে গিয়ে রশিই ছিঁড়ে না যায় সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে।
সর্বশেষ ব্যবস্থা হল শারীরিক শাস্তি। সর্বাপেক্ষা বেশি সতর্কতা এ ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। বিবেচনা করতে হবে, অন্যায়টি শারীরিক শাস্তির উপযুক্ত কি না। এ ব্যাপারে বয়স-বিচার গুরুত্বপূর্ণ। শিশুবয়সের কিছু স্বাভাবিক আচরণ থাকে। তাকে বয়ষ্কের দৃষ্টিতে বিচার করা চলে না। শুধুশুধুই হৈহল্লা করা, ছোটাছুটি করা, খেলাধুলায় মেতে ওঠা এবং এজাতীয় অনেক কাজ আছে, যা খুব বেশি বাড়াবাড়ির পর্যায়ে না হলে শাস্তির আওতায় আনা ঠিক না। শিশুর দেহ-মনের বিকাশের জন্য ওগুলোরও প্রয়োজন আছে। তাই শাস্তি দেওয়া তো নয়ই, বরং সর্বক্ষণ আবদ্ধ না রেখে সুনির্দিষ্ট সময়ে এরও সুযোগ করে দেওয়া চাই। সারকথা শৈশবের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলোকে উদার দৃষ্টিতেই দেখতে হবে।
যথার্থই যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, সে ব্যাপারেও বয়স-বিচার জরুরি। যাতে সীমালংঘন না হয়ে যায়। পনের-ষোল বছর বয়সের বালককে যে মাত্রায় মার দেওয়া যায়, আট-দশ বছরের শিশুর জন্য তা প্রযোজ্য নয়।
শারীরিক শাস্তিদানকালে আত্মনিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। রাগ দমন করে ঠাণ্ডা মাথায় শাস্তি দেওয়া উচিত। যাতে মারটাও হয় দরদের সাথে। মনে রাখতে হবে-
‘দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা যবে কাঁদে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার’।
উদ্দেশ্য যখন শোধরানো, তখন মারের সাথে বেদনার প্রকাশ থাকতেই হবে।
প্রকাশ থাকে যে, মার হাতেও দেওয়া যায়, তবে লাঠি ব্যবহারই উত্তম। হাতে মারলেও অর্থাৎ চড়-থাপ্পর দিলে তা চেহারায় কিছুতেই নয়। হাদীসে সুস্পষ্ট নিষেধ আছে। লাঠি ব্যবহারে ইদানীং নেতিবাচক দৃষ্টিভংগীর বাড়াবাড়ি আছে। অনেকে মনে করে লাঠি ব্যবহার কিছুতেই উচিত নয়, কিন্তু এটা ভুল ধারণা। প্রয়োজনস্থলে বেত ব্যবহার না করাও এক ধরনের শিথিলতা। এতে অন্যায়কারী প্রশ্রয় পায় এবং সে ধৃষ্ট ও স্পর্ধিত হয়ে ওঠে। বস্তুত কোনও ধরনের প্রান্তিকতা কল্যাণকর নয়।
তবে একথাও সত্য যে, লাঠি ব্যবহার খুবই স্পর্শকাতর কাজ। বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে তা দুনিয়া-আখিরাত উভয়স্থলের জন্য ক্ষতিকর। এটা হক্কুল-ইবাদের অন্তর্ভুক্ত। আখিরাতে এর জন্য জবাবদিহিতার ভয় আছে। তাই আগেই যে কথা বলা হয়েছে, উত্তেজিত অবস্থায় প্রহার পরিত্যাজ্য। গায়ের শক্তি দিয়ে মারা যাবে না; বরং যাকে মারা হচ্ছে তার সহনক্ষমতাও লক্ষণীয়। এমন জোরে মারা জায়েয নয়, যদ্দরুণ গায়ে কালো দাগ পড়ে যায়। যখম করে ফেলার তো প্রশ্নই আসে না। লাঠি খুব মোটা ও ভারী হওয়াও উচিত নয়। এবং ছোট-চিকন লাঠি দ্বারাও অনবরত পেটাতে থাকা বৈধ নয়। দু-চার বেত দিয়েই ক্ষান্ত করা উচিত। অর্থাৎ মোটামুটি কষ্ট পায় এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে যায় এ পরিমাণ মারই যথেষ্ট।
মারের আগে নিজেকেও বিচার করে দেখতে হবে, কেবলই গোস্বার কারণে মারা হচ্ছে, না ইসলাহ ও সংশোধনের প্রয়োজনে। অর্থাৎ বৈধ হওয়ার জন্য নিয়ত খালেস থাকা শর্ত। খালেস নিয়তে মাত্রাজ্ঞানের সাথে বেত্রাঘাত করা হলে তা অবশ্যই সুফল বয়ে আনবে। কিন্তু মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় ঠিক ক’জন দেয়? আমার ওই স্নেহভাজন শিশুটির ক্ষেত্রেও সে পরিচয় পাওয়া যায়নি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, ভাইয়া পালালে কেন? ‘খুব মারছিল- ও বলল, একবার পিটানি দিলে আমি একটু পিছিয়ে গিয়েছিলাম। তাই উঠে অনেক মেরেছে।’ তার পরের দিন আবার পরীক্ষা’। মারের যন্ত্রণায় পিছিয়ে গিয়েছিল। এটা তার বেআদবী! তাতে মারার সুবিধাও বিঘিœত হয়েছিল। ডবল অপরাধ। বাছা, শায়েস্তা তো তোমাকে হতেই হবে। কিন্তু না, এভাবে শায়েস্তা করা সংগত নয়। মানুষ গড়ার মহান মেহনতকে সিদ্ধ- ও শুদ্ধ পন্থায়ই আন্জাম দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।