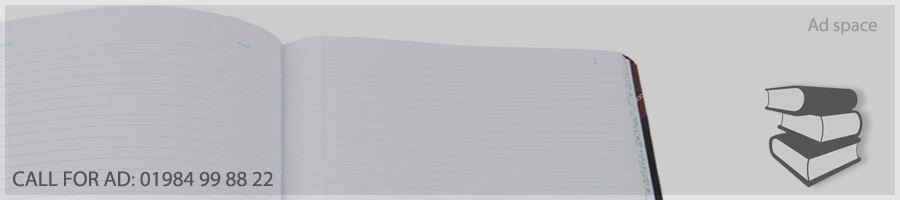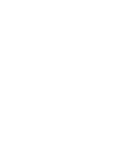তুরস্কে, তুর্কিস্তানের সন্ধানে-৬
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
***
মুহাম্মদ আলফাতিহ-এর প্রাসাদের সামনে ঝান্ডাস্থাপনের যে উঁচু স্থান সেখানেই উছমানী সালতানাতের পরবর্তী শাসকগণ খেলাফতের বাই‘আত গ্রহণ করতেন।
আরেকটু অগ্রসর হলে আরেকটি দরজা। এ দরজা পার হলেই দেখা যায় বড় বড় কয়েকটি কামান। গাইড সবচে বড় কামানটি দেখিয়ে বললেন, ইস্তাম্বুল দখল করার জন্য সুলতান বিশেষভাবে এ কামানটি তৈরী করেছিলেন, যা তখনকার সামরিক বিশ্বে ছিলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তখন সবচে’ বড় কামানের পাল্লা ছিলো একমাইলের কিছু কম, আর এ কামানের পাল্লা ছিলো এক মাইলেরও বেশী। একেকটি গোলার ওজন ছিলো পাঁচশ’ কিলোগ্রাম-এরও বেশী।
মনে পড়ে, আমরা যখন ছোট, ঢাকার গুলিস্তানের মোড়ে দু’টি কামান ছিলো। বলা হতো, মিরজুমলার কামান। বড় হয়ে দেখেছি, কামানদু’টি আর গুলিস্তানের মোড়ে নেই, সোহরোয়ার্দি উদ্যানে আশ্রয় নিয়েছে। এখন সেগুলি ওখানে আছে কি না বলতে পারি না। সুলতান মুহাম্মদের এই কামানের সামনে ঐ দু’টিকে মনে হবে ‘দুধ কা বাচ্চা’।
ইস্তাম্বুল বিজয়ের স্মারক কামানটির সামনে দাঁড়িয়ে অন্তরে যে পুলক-শিহরণ সৃষ্টি হলো তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যেন কল্পনার চোখে নয়, বাস্তবেই দেখতে পাচ্ছি, দূর অতীতের সেই জিহাদের আগুন-তুফানের গৌরবময় দৃশ্য। এই যে কামান থেকে গোলা বের হলো, পাচিলের গায়ে গিয়ে আঘাত করলো, বিস্ফোরণের প্রচন্ড শব্দে নগরদুর্গ কেঁপে উঠলো; জোশে উদ্দীপনায় নিজের অজামেত্মই বলে উঠলাম, আল্লাহু আকবার! কাছাকাছি যে ক’জন ছিলেন, অবাকচোখে আমার দিকে তাকালেন! আমার মুখে তখন অপ্রতিভ হাসি। নিজেকে অপ্রস্তুত মনে হলো। সত্যি তাই; কারণ কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে যে বসফরাস সাগরের ব্যবধান!
কামানটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবছি, এই কামানের কথা প্রথম কোথায় যেন পড়েছি! মনে পড়লো, আমার প্রিয়তম সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ.-এর লেখায় পড়েছিলাম।
ভীষণ ইচ্ছে করছিলো, একটু স্পর্শ গ্রহণ করি। গর্ব করে বলতে পারবো আমার পরবর্তী প্রজন্মকে, আমার ছেলেমেয়েকে, আমার ছাত্রদেরকে, যে কামানের গোলা ইস্তাম্বুলের পাচিল গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো তার স্পর্শ রয়েছে আমার হাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাত এগুলো না। মনে হলো আমরা এর যোগ্য নই। আমাদের স্পর্শে এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে।
গাইড ততক্ষণে সামনে এগিয়ে গেছেন। অপেক্ষাকৃত ছোট আরেকটি কামান দেখিয়ে তিনি বললেন, ‘সুলতান সোলায়মান ভিয়েনা অবরোধকালে এ কামান ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বৈরী আবহাওয়ার কারণে তাঁকে অবরোধ তুলে ফিরে আসতে হয়েছিলো, নইলে আজ ইতিহাসের চেহারা অন্যরকম হতো।’
আসলে ইতিহাসের চেহারা সবসময় ইতিহাসের মতই হয়, অন্যরকম হয় না। চেহারার রূপ বদল হয় মানুষের এবং তাদের শাসকদের। ইতিহাস শুধু নিজের আয়নায় সেই চেহারাগুলো তুলে ধরে। মানুষ নিজেকে বদল করলেই শুধু ইতিহাসের রূপবদল হয়, উত্থানের দিকে, কিংবা পতনের দিকে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। যদিও বারবার ব্যবহারের কারণে কথাটার ধার ও ভার মরে গেছে, কিন্তু কথাটা এখনো সমান সত্য, তাই বলতেই হয়, ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, মানুষ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। সোলায়মান অনেক ভালো শাসক ছিলেন, কিন্তু কিছু অন্যায়ও করেছেন, যার মাশুল দিতে হয়েছে তাঁর উত্তসূরীদের। অনেক অন্তর্দর্শী তো বলেন, আসলে সোলায়মানের শাসনকালেই সবার অলক্ষ্যে উছমানী সালতানাতের পতনের বীজবপন হয়ে গিয়েছিলো। কালে কালে তা অঙ্কুরিত ও বিস্তৃত হয়েছে, আর শেষ পর্যন্ত ১৯২৪ সালে মুস্তফা কামাল পাশার হাতে তা ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছেমাত্র। এই কামানটিকে অবশ্য আলতো করে একটু ছুঁলাম। তার শীতল স্পর্শেও যেন ছিলো একটু উষ্ণতা।
***
গাইডকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম; কারণ সর্বপ্রথম তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন ঐ কক্ষে যেখানে সংরক্ষিত রয়েছে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু তাবাররুক। পুরো কক্ষ উদ-এর সুগন্ধিধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। প্রবেশ করামাত্র দেহ-মন সর্বসত্তা যেন সুরভিত হয়ে গেলো। ধোঁয়া, সুগন্ধির হলেও আমার ভালো লাগে না; কেমন যেন দম আটকে আসে, কিন্তু আজ এখানে হলো অন্যরকম। এ সুগন্ধিধোঁয়ার মধ্যে ইচ্ছে করেই গভীরভাবে শ্বাস নিলাম; শান্তি লাগলো, নিজেকে পরিচ্ছন্ন ও
পবিত্র মনে হলো।
এখানে সংরক্ষিত রয়েছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুববা মোবারক, দান্দান মোবারক, দাড়ি মোবারক; দু’টি তলোয়ার, একটি ঝান্ডা, যা বদরের গাযওয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে বলে কথিত; আর রয়েছে মিশরের শাসক মাকাওকিসের নামে প্রেরিত তাঁর মোহরাঙ্কিত পবিত্র চিঠি।
এগুলো কোনটিই উন্মুক্ত অবস্থায় নেই। মূল্যবান কাঠের সুদৃশ্য পাত্রে আবদ্ধ।
গাইড বললেন, বছরে একবার, মাত্র একবার সাতাশে রামাযান রাত্রে উন্মুক্ত অবস্থায় এগুলো প্রদর্শিত হয়। যে ভাগ্যবানেরা তখন উপস্থিত থাকেন, চোখ আলোকিত করে তা দেখতে পান। এখন শুধু কাঠের বাক্সগুলোই যিয়ারত করা যেতে পারে।
আল্লাহ তা‘আলা হযরত মাওলানা তাক্বী উছমানীকে উত্তম বিনিময় দান করুন, এখানে এসে কত সুন্দর কথা লিখেছেন-
‘আমরা শুধু দূর থেকে কাঠের বাক্সগুলোই দেখতে পেলাম। আমাদের গোনাহগার চোখ তো আসলে ঐ তাবাররুক অবলোকন করার যোগ্যই ছিলো না; যে বাক্সগুলো ঐ তাবাররুকের স্পর্শলাভে ধন্য হয়েছে তা দেখতে পাওয়াই তো আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয়।’
আসলে এভাবে চিন্তা করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব, আল্লাহ যাকে দান করেছেন আশিক দিল ও প্রেমিক হৃদয়।
প্রশ্ন হলো তাহকীক ও গবেষণার দিক থেকে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এগুলোর সম্পৃক্তি কতটা প্রমাণিত? এ প্রশ্নের জওয়াবও আল্লামা উছমানী মু. দিয়েছেন। প্রথমত, দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সম্পৃক্ত যত তাবাররুক রয়েছে, তুলনামূলকভাবে প্রামাণ্যতার দিক থেকে ইস্তাম্বুল সবার উপরে।
আর শুধু এ সম্ভাবনাটুকুই কি দিলের দরিয়ায় মউজ পয়দা করার জন্য যথেষ্ট নয় যে, হতেও তো পারে!
আবারও বলি, আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন হে তাক্বী! হে উছমানী!!
ছোট্ট একটি কক্ষে শতাধিক মেহমান প্রবেশ করছেন, অবলোকন করছেন, তারপর বের হচ্ছেন, এর মধ্যে প্রাণ শীতল করা বিষয় এই যে, কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই আশ্চর্য রকম ভাবগম্ভীর! কারো চোখে অশ্রু, কারো চেহারায় কান্না চেপে রাখার স্পষ্ট প্রয়াস। কান্নার আওয়াযও যেন আদবের খেলাফ! আশ্চর্য এক মৌনতা ও নৈঃশব্দের মাঝে ভেসে আসছে কারো কণ্ঠের সুমধুর তেলাওয়াত। এবং আল্লাহর কী মহিমা! তখন তেলাওয়াতের আয়াত ছিলো-
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
‘নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফিরেশতাগণ নবীর উপর ছালাত প্রেরণ করেন, হে মুমিনগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি প্রচুর ছালাত ও সালাম প্রেরণ করো।’
হঠাৎ মৃদুমধুর একটি গুঞ্জন হলো, আল্লাহুম্মা ছাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদ ...
এসকল পবিত্র তাবাররুক মূলত আববাসী খলীফাদের তত্ত্বাবধানে ছিলো, যা হতে হতে নামসর্বস্ব সর্বশেষ খলীফা মুতাওয়াক্কিল[1]-এর কাছে এসে পৌঁছে। বেচারা তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো পার করছিলেন মিশরে মমলূকদের আশ্রয়ে, না ছিলো রাজ্য, না ছিলো রাজকর্তৃত্ব; এমনকি সাধারণ কোন ক্ষমতাও ছিলো না। হিজরী দশম শতকে হিজায ও মিশরের সমগ্র অঞ্চল যখন উছমানী সুলতান প্রথম সেলিম-এর অধিকারে এসে গেলো এবং তিনি ‘খাদেমুল হারামাইন’ খেতাব লাভ করলেন, এই বেচারা খলীফা তখন খেলাফতের পদটিও সুলতানকে সঁপে দিলেন। না দিয়ে উপায়ও ছিলো না, কারণ তাঁর দুর্বল কাঁধ তখন ঐ পবিত্র পদ-এর ‘নাম-ভার’টুকুও বহন করার উপযুক্ত ছিলো না। তখন তিনি খেলাফতের নিশানরূপে হারামাইনের চাবিসহ এসব তাবাররুকও সুলতানের হাতে সোপর্দ করে দেন। এভাবে সুলতান সেলিম-এর সময় থেকে ‘উছমানী খিলাফত’ বলা শুরু হয় আর তুর্কী সুলতানগণ খলীফা ও আমীরুল মুমিনীন উপাধি ধারণ করেন। সমগ্র মুসলিম জাহানও জাগতিক শাসনের পাশাপাশি তাদের এ আধ্যাত্মিক মর্যাদা মেনে নেয়।
সুলতান সেলিম যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে এসকল তাবাররুক মিশর থেকে ইস্তাম্বুল আনার ব্যবস্থা করেন। সুলতানের অন্তরে এসকল তাবাররুকের এমনই কদর-মুহববত ও মর্যাদা-ভালোবাসা ছিলো যে, তিনি নিজের হাতে তাবাররুকের কামরা ঝাড়ু দিতেন। তাছাড়া তিনি দিন-রাত পালাক্রমে হাফিযদের সার্বক্ষণিক তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তী খলীফাগণও এ ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এভাবে সম্ভবত দুনিয়ায় এটাই ছিলো একমাত্র স্থান যেখানে সুদীর্ঘ চারশ বছর পর্যন্ত ধারাবাহিক- ভাবে কোরআনুল কারীমের ‘খতমতিলাওয়াত’ চলে এসেছে। মুস্তফা কামাল পাশা যখন উছমানী খেলাফতের গলায় ছুরি চালিয়ে তুরস্কের ‘সাদা-কালো’ সবকিছুর মালিক-মুখতার বনে গেলেন তখন হয়ত ধর্মবিমুখ আধুনিক তুরস্ক গড়ার পথে অন্তরায় মনে করে এ কল্যাণধারা বন্ধ করে দেন। আল্লাহ তাকে, কী করুন, বলবো! ‘মাফ করুন’ই বলি!!
গাইড বললেন, নাজমুদ্দীন আরবেকানের সময় তেলাওয়াতের ধারা পুনঃপ্রবর্তিত হয়, যা এখন পর্যন্ত চলছে। এটা অবশ্য সত্য যে, তিলাওয়াত নিজস্ব সত্তায় ইবাদত হলেও এর ধারাবাহিকতা শরীয়তের কোন আদেশ নয়, তবে এর কল্যাণ-করতায়ও সন্দেহ নেই।
কাতারে দাঁড়িয়ে এক দরজা দিয়ে মেহমানরা প্রবেশ করছে, তারপর ধীরে ধীরে অন্য দরজা দিয়ে পাশের কামরায় যাচ্ছে, সেই ধারাবাহিকতায় আমরাও গেলাম। দ্বিতীয় কামরায় সবকিছু কাঁচের পাত্রে রাখা ছিলো। গাইড বললেন, এই চারটি তলোয়ার যথাক্রমে খোলাফায়ে রাশেদীনের; আর এটা হচ্ছে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের তলোয়ার।
একটি অংশে ছিলো গিলাফে কা‘বার একটি খন্ড, কা‘বা শরীফের দরজা ও মীযাবে রহমতের অংশবিশেষ, কা‘বার তালা ও চাবি; এছাড়া ঐ থলি যার ভিতরে কোন একসময় হজরে আসওয়াদ রক্ষিত ছিলো। একটি সোনার পাত্রে কিছু মাটি ছিলো, গাইড বললেন, এটা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা শরীফের মাটি।
কামরার শেষ দিকে বের হওয়ার যে দরজা, তার লাগোয়া অংশে কাঁচের আধারে ছিলো একটি ছোট জামার অংশবিশেষ। গাইড বললেন, এটা হযরত হাসান, বা হোসাইন রা.-এর শৈশবের জামা, যা মা ফাতেমা রা. নিজ হাতে সেলাই করেছেন। শোনামাত্র বুকের মধ্যে আশ্চর্য এক কম্পন অনুভূত হলো। কল্পনায় ভেসে উঠলো ইমাম হাসান-হোসায়নের শৈশবের ছবি যখন তাঁরা মদীনার ধূলোবালিতে খেলা করতেন। প্রিয় নানা তাঁদের কাঁধে করে মদীনার পথে হাঁটতেন। আরো ভেসে উঠলো সেই পবিত্র দৃশ্য যখন শিশু হাসান, বা হোসায়ন ছোট ছোট পা ফেলে হেঁটে আসতেন, আর পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে এসে আদরের নাতিকে কোলে তুলে নিতেন।
গাইড বললেন, ঐ যে দেখছেন, সেটি হযরত ফাতেমা রা.-এর দোপাট্টা। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ অবনত হলো। সত্যি যদি এটা পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা, জান্নাতের নারীদের সরদার হযরত ফাতেমা রা.-এর পবিত্র দোপাট্টা হয়ে থাকে তাহলে তো সেদিকে নেগাহ তুলে তাকানোটা হবে চরম বেয়াদবির শামিল। আসলে এটা এভাবে রাখাটাও বোধহয় আদবের খেলাফ।
***
শরীয়তের দৃষ্টিতে আমলই হচ্ছে আসল। আমলের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয় আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা। তাই তো এত সমস্ত তাবাররুকের আমানতদার হয়েও আববাসী খলীফাকে ভোগ করতে হয়েছে যিলস্নতির জীবন। এ চিন্তা আমাকে এমনই উদ্বেলিত করলো যে, তখনই প্রতিজ্ঞা করলাম, যত দিন বেঁচে আছি পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর জীবন যাপন করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবো। আল্লাহ যেন তাওফীক দান করেন, আমীন।
***
এরপর আমরা যে প্রাসাদে গেলাম, উপরে নীচে তাতে রয়েছে বড় বড় অনেক কক্ষ। প্রতিটি কক্ষে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার ঐতিহাসিক দ্রব্যসম্ভার। প্রথম যে কক্ষে প্রবেশ করলাম সেটি হলো অস্ত্র-কক্ষ। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন যুগের ছোট বড় অসংখ্য যুদ্ধাস্ত্র। তীর-ধনুক, ঢাল-তলোয়ার, খঞ্জর, কুঠার ও লৌহবর্মসহ জানা-অজানা বহু সরঞ্জাম।
একটি ভাঙ্গা ধনুক দেখিয়ে গাইড বললেন, পারস্যের শিয়া বাদশাহ ইসমাঈল এটি পাঠিয়েছিলেন সুলতান সেলিমের দরবারে এই পায়গামসহ যে, আপনার দেশের কোন বীর যুবককে বলুন, এটি ভাঙ্গতে পারে কি না! সুলতানের সত্তর বছর বয়সী উযীর ধনুকটি হাতে নিয়ে একটা চাপ দিতেই ভেঙ্গে গেলো। সুলতান তখন দূতমারফত বলে পাঠালেন, এ ধনুক তো আমার বুড়ো উযিরের হাতেই টিকলো না। আমার দেশের জোয়ানদের জন্য আরো মযবুত ধনুক পাঠিয়ে দিন।
একটি খঞ্জর দেখলাম, মুক্তাখচিত, গাইড বললেন, এই যে তিনটি পাথর, এগুলো হচ্ছে যমররুদ, অতি মূল্যবান পাথর। এটি নাকি সুলতান মুহাম্মদ-এর ব্যবহৃত খঞ্জর। বলা হয়, এটি হচ্ছে পৃথিবীর সবচে’ মূল্যবান খঞ্জর। আমার বলতে ইচ্ছে করলো, অস্ত্রের মূল্য তো আসলে তাতে যুক্ত সোনাদানা, হীরা-জহরত দ্বারা হয় না, হয় ব্যবহারকারীর কব্জির তাকত দ্বারা।
হিন্দুস্তানের দরবেশ বাদশাহ, যিনি জীবনের সিংহভাগ সময় কাটিয়েছেন ঘোড়ার পিঠে, জিহাদের ময়দানে; একের পর এক বিদ্রোহ দমনেই যাকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছে বেশীর ভাগ সময়, যে বিদ্রোহ ছিলো আপনপর, শত্রম্নমিত্র উভয়ের পক্ষ হতে। তাঁকে নাকি একবার কোন বিদ্রোহী রাজপুত সেনাপতি একটি মুক্তাখচিত খঞ্জর উপহার পাঠিয়েছিলেন বিদ্রূপ করে, আর তিনি খঞ্জর ফেরত পাঠিয়ে বলেছিলেন, মুক্তাগুলো মালায় গেঁথে গলায় পরুন, আমাকে শুধু খঞ্জরটি পাঠিয়ে দিন, শুকরিয়ার সঙ্গে গ্রহণ করবো।
আরেকটি ঘটনা আছে চরম দুর্যোগকালে হিন্দুস্তানের আযাদীর জন্য জান বাজি রেখে লড়াইকারী শেরে মহিসুর সুলতান ফতেহ আলী খান টিপু সম্পর্কে। হায়দারাবাদের নেযাম একটি তলোয়ার পাঠিয়েছিলেন সোনার কারুকাজযুক্ত। তিনি হাদিয়া কবুল করে, একটি সাধারণ, কিন্তু মযবূত তলোয়ার ফিরতি উপহার পাঠিয়েছিলেন এই বলে, কারুকাজের তলোয়ার শুধু কোমরের শোভা বর্ধন করে, দুশমনের বিরুদ্ধে তেমন কাজে আসে না, আমার তলোয়ার আপনার কাজে আসবে, যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে ময়দানে লড়াই করার হিম্মত রাখেন।
তো মুক্তাখচিত খঞ্জরটি দেখে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হলো না, এটি সুলতান মুহাম্মদ ব্যবহার করতেন। কারণ তিনি ছিলেন সত্যিকারের বাহাদুর সিপাহী। এটি হয়ত পরবর্তী কোন খলীফার হবে। একটি কক্ষে ছিলো বিভিন্ন সুলতানের ব্যক্তিগত লেবাসপোশাক। সবগুলো পোশাক কালক্রম অনুসারে সাজানো। একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেলো, প্রথম দিকে সুলতানদের লেবাসপোশাক ছিলো খুব সাধারণ। হীরামুক্তার ব্যবহার ছিলো না বললেই হয়। বিশেষ করে সুলতান মুহাম্মদের লেবাস ছিলো একেবারেই সাধারণ। তাঁর একটি আবা দেখে যে কারোই মনে হবে, এটি যিনি ব্যবহার করতেন, নিশ্চয় তিনি ছিলেন যামানার দরবেশ।
পক্ষান্তরে সময় যত এগিয়েছে, লেবাসপোশাকে ততই জৌলুস ও জাঁকজমক এসেছে।
***
আমাদের গাইড তরুণ তুর্কী আলিম। তার দ্বীনী গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ সত্যি প্রশংসনীয়। তিনি আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন, এখন আমি আপনাদের যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সাধারণ পর্যটকদের কাছে সেগুলোর আকর্ষণই সবচে’ বেশী। কিন্তু আমি আপনাদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছি শুধু ইবরত ও শিক্ষাগ্রহণের জন্য। নচেৎ এগুলো দেখা, আর সময়ের অপচয় করা সমান কথা, তার চেয়ে বরং হোটেলের কামরায় অবস্থান করা, বা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বসফরাসের ঢেউ দেখা ঢের ভালো।
তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন ঐ সুপরিসর কক্ষে যেখানে সংরক্ষিত ছিলো বেশ কিছু সিংহাসন, রাজমুকুট, গয়না-অলঙ্কার এবং দুর্লভ পাথর ও হীরা-জহরত।
গাইডের হেদায়েতমত ইবরতের নযরেই সবকিছু দেখছিলাম।
হঠাৎ দেখি গাইড আমার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন, জিজ্ঞাসা করলাম, কী দেখছো! বললেন, দেখছি তোমাকে, আর ভাবছি, তুমি বোধহয় দেখার মত করেই দেখছো!
আমি মৃদু হেসে বললাম, আচ্ছা বলতে পারো, এই যে এত রাজা-বাদশাহর এত সিংহাসন, আবু বকর, ওমর, উছমান, আলী, এঁদের সিংহাসন কোথায়? কিংবা উমর বিন আব্দুল আযীয? অন্তত সুলতান সালাহুদ্দীন?
তিনি মুহূর্ত বিলম্ব না করে, যেন এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং উত্তরও প্রস্তুত ছিলো, ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ ওজনদারভাবে উচ্চারণ করে বললেন, তাঁদের একটিমাত্র সিংহাসনে চলবে কেন! তাঁদের জন্য তো প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে রয়েছে একটি করে সিংহাসন। আর হৃদয়ের সিংহাসনে যারা সমাসীন, স্বর্ণ-রৌপ্য ও হীরাজহরতের সিংহাসন তাদের কাছে মূল্যহীন।
কয়েকটি রাজমুকুটও ছিলো।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সুলতান মুহাম্মদ আলফাতিহ-এর মুকুট কোথায়?। গাইড বললেন, ‘তাঁর তো কোন মুকুট ছিলো না, তিনি শুধু ‘আমামা’ ধারণ করতেন! আসলে আমার প্রশ্নটাই ছিলো ভুল। ইস্তাম্বুল জয়ের মুকুট তাকদীর যার মাথায় রেখেছে, তাঁর তো কোন রাজমুকুটের প্রয়োজনও ছিলো না!
একটি বড় কাঁচের আধারে কয়েকটি শামাদান, আগরদান ও গুলদান সাজিয়ে রাখা হয়েছে। গাইড বললেন, এগুলোতে স্বর্ণ ছাড়া আর কিছু ব্যবহার করা হয়নি! কোনটারই ওজন আধামনের কম হবে না। আল্লামা তাক্বী উছমানী মু. লিখেছেন, ‘ডায়মন্ড বা হীরা, এর আগে শুধু নামই শুনেছি, আসল হীরা কখনো এ পোড়া চোখে দেখার সুযোগ হয়নি। এখানে এসে দেখলাম বেশ বড়, সুন্দর এবং ঐতিহাসিক একটি হীরা।’
বলাবাহুল্য, আমার মত গোবেচারা মানুষের ক্ষেত্রে তো এ কথা আরো সত্য। তবে কুহ-ই-নূরের ছবি দেখেছি, যা সঠিক শব্দে যদি বলি, ইংরেজরা হিন্দুস্তান থেকে ‘চুরি’ করে নিয়ে গেছে এবং এখন তা তাদের রানীর মুকুটে শোভা পাচ্ছে। ‘শোভা’ শব্দটির ব্যবহার এখানে হয়ত ঠিক হলো না। চুরির মাল কখনো শোভা পায় না। পত্রিকায় পড়েছি, ভারত সরকার নাকি ইংল্যান্ডের কাছে কুহ-ই-নূর ফেরত চেয়েছে! এ দেখি আরেক তামাশা! চোরের উপর তস্কর! কুহ-ই-নূর ভারত দাবী করবে কোন্ যুক্তিতে! তাজমহল না হয় পেয়ে গেছে স্থাবর সম্পত্তি হিসাবে ভৌগোলিক দখলদারিত্বের সুবাদে, কিন্তু কুহ-ই- নূর! এ তো আগাগোড়া মুসলমানদের অস্থাবর সম্পত্তি!
যাক, ফিরে আসি আগের কথায়, জীবনে এই প্রথম দেখলাম আসল হীরা। আকারে এটি কিসের মত বলা যায়! আল্লামা তাক্বী উছমানী মু. বলেছেন চামচের মত ... আকারের। আমার মনে হয়, একটি সেদ্ধ ডিম লম্বায় দু’ভাগ করলে যেমন দেখায়, এ ঠিক তেমন, তবে কুসুমের রঙটা এখানে নেই। ওজনে ছিয়াশি ক্যারেট। এর চারপাশে এমন কুশলতার সঙ্গে সোনার ফ্রেম যুক্ত করা হয়েছে যে, বুঝি তা হীরকখন্ডেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ! গাইড বললেন, অন্ধকারেও তা থেকে হালকা আলো বিচ্ছুরিত হয়। আমাদেরও দেখে এত ঝলমলে মনে হলো, যেন স্ফটিকের পাত্রে অদৃশ্য কোন বাল্ব জ্বলছে। শুনলাম, এ থেকে যে আলো প্রতিফলিত হয়, যদি সমকোণে দাঁড়িয়ে দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে দৃষ্টি ধাঁধিয়ে যায়।
কুহ-ই-নূরের মত এই হীরকটিরও রয়েছে ইতিহাস, তবে তার গায়ে তেমন কোন রক্ত জড়িয়ে নেই, আছে শুধু একটি মাতৃহৃদয়ের মমতা। এ কারণে এটি দেখে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়নি, বরং মনটা ভিতরে ভিতরে কেমন করে উঠেছিলো।
এমনিতে পৃথিবীতে বিখ্যাত যত হীরকখন্ড রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোন না কোন রক্তপাতের কাহিনী। তাই প্রতিটি হীরকখন্ডকেই আমার মনে হয় অভিশপ্ত।
সে যাক, অর্ধডিম্বাকৃতির এ হীরকখন্ডটির আদি মালিক ছিলেন ভারতবর্ষের কোন মহারাজা। জনৈক ফরাসি জেনারেল তা খরিদ করে ফ্রান্সে নিয়ে যান। কয়েকটি হাত হয়ে সেটি যায় সুপ্রসিদ্ধ বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মায়ের হাতে। কথিত আছে, তিনি বলেছিলেন, প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু এ হীরকখন্ডটি নয়। তাঁর কথা হয়ত সত্য ছিলো, কিন্তু প্রাণের চেয়ে মূল্যবান কিছু্ও তো আছে পৃথিবীতে, যার জন্য এমন দশটি হীরকখন্ড অকাতরে হাতছাড়া করা যায়!
এখানেও তাই ঘটলো।
ওয়াটার লু যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হয়ে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তখন নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। পুত্রকে ইংরেজ-নির্যাতনের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য মায়ের তখন বিপুল অর্থের প্রয়োজন। ইংরেজরা তেমন প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলো। আশ্চর্য, প্রতিবেশী হয়েও ইংরেজদের ধূর্ততা ও প্রতারণার কথা তিনি জানতেন না! অথবা জানতেন, তবু মাতৃহৃদয় হয়ত দুরাশাকেও আশা ভাবতে বাধ্য হয়েছিলো।
সে যাক, নেপোলিয়ানের মা ঐ হীরকখন্ড তুর্কী জেনারেল আলী পাশা-এর কাছে বিক্রি করেন দেড় শ মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে। জেনারেল আলী পাশার কাছ থেকে স্বাভাবিক কারণেই তা চলে আসে উছমানী সুলতানের হাতে। আর এখন তা এই তোপকাপে মিউজিয়ামের শোভা বর্ধন করছে।
দাবীকৃত অর্থ পেয়ে ইংরেজরা কি শেষ পর্যন্ত মাতৃহৃদয়ের আকুতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলো? দূর, তাহলে ইংরেজ আর ইংরেজ হবে কেন! ভারতবর্ষই বা মুসলমানদের হাতছাড়া হবে কেন!!
মুকুট ও সিংহাসনের কক্ষ থেকে আমরা আরেকটি কক্ষে গেলাম যেখানে শুধু ঐ সব উপহার ও উপঢৌকন সংরক্ষিত ছিলো যা বিভিন্ন সময় ইউরোপের বিভিন্ন রাজা-রানী উছমানী সুলতানদের দরবারে প্রেরণ করতেন। তাকালে শুধু তাকিয়েই থাকতে হয়। পরিমাণে যেমন বিপুল তেমনি প্রতিটি দ্রব্য সৌন্দর্যে, শিল্পসৌকর্যে এবং অর্থমূল্যে অসাধারণ।
রাজ্যে রাজ্যে এবং রাজায় রাজায় উপহার বিনিময়ের যে রীতি প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে তার মূলে রয়েছে হয় বন্ধুত্বের প্রকাশ, কিংবা বশ্যতার স্বীকৃতি। তো সে যুগে বিশ্বের রাজদরবার-গুলোতে একটা কথা প্রচলিত ছিলো, ‘তুর্কী সুলতান উপঢৌকন প্রেরণ করেন না, শুধু গ্রহণ করেন’। কারণ প্রকৃত অর্থে তুর্কী সুলতানের কোন বন্ধু ছিলো না, বিশেষ করে ইউরোপে, আর কোন রাজা বা রাজ্যের প্রতি সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করার তো প্রশ্নই ছিলো না। তাই ভীত সন্ত্রস্ত ইউরোপীয় নৃপতিগণ সুলতানের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বলতে গেলে প্রতিযোগিতামূলক- ভাবেই উপহার-উপঢৌকন প্রেরণ করতেন, আর প্রত্যেকেই চেষ্টা করতেন, যেন তার উপহার সুলতানের মনোযোগ ও কৃপাদৃষ্টি অধিক আকর্ষণে সক্ষম হয়।
সবচে’ ছোট উপহারদ্রব্যটি হলো সুরমাদানি, দেখতে যা ছোট্ট ময়ূর আকৃতির। চোখ দু’টো দূর থেকেও মনে হলো জ্বলজ্বল করছে। কী পাথর, কে জানে! ময়ূর যেন পেখম মেলে আছে, আর পুরো পেখম সাজানো হয়েছে বিভিন্ন বর্ণের হীরা, জহরত, ইয়াকুত ও পান্না দ্বারা, যাতে ময়ূরপেখমের প্রাকৃতিক রূপটি ফুটে ওঠে। নাহ, যিনি এটা প্রেরণ করেছেন তার রুচিবোধ এবং যে কারিগর তৈরী করেছেন তার শিল্পবোধের প্রশংসা করতেই হয়।[2]
সবচে’ বড় উপঢৌকনটি হলো ‘ঝাড়বাতি’ যা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে কক্ষটির ঠিক মাঝখানে। কথিত আছে, এতে এমন কারিগরি প্রয়োগ করা হয়েছে যে, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তা ধীর লয়ে ঘুরতে থাকতো, কিন্তু বাতিগুলো থাকতো স্থির, ফলে হীরা-জহরত-গুলো আলোর প্রতিফলনে ঝলমল করতো।
টিয়ে বা ময়নাজাতীয় একটি পাখীও দেখলাম, পুরোটাই পাথরে তৈরী। গাইড বললেন, আসলে এটা উপঢৌকন নয়, ছিলো একটা কূট চক্রামেত্মর বাহন। পাখীটার পেটের অংশে বোতাম ছিলো; তাতে টিপ দিলে আতর ছিটিয়ে বের হতো। এর ভিতরটা এমনভাবে বিষমিশ্রিত করা হয়েছিলো যে, আতরের ঘ্রাণের সঙ্গে বিষও ব্যবহারকারীর ভিতরে চলে যাবে। বিষের ক্রিয়া হবে এত ধীরে সন্তর্পনে যে, কেউ বুঝতেই পারবে না, কীভাবে মৃত্যু হলো। এটা ছিলো সুলতানকে হত্যা করার একটা ঘৃণ্য চক্রান্ত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সুলতান এটা ব্যবহারই করেননি, তিনি তার এক প্রিয় দাসীকে এটা উপহার দিয়েছিলেন, আর ঐ দাসী ধীরে ধীরে বিষক্রিয়ার শিকার হয়েছিলো। সুলতানের বিজ্ঞ চিকিৎসক বিষয়টি ধরতে পেরেছিলেন, কিন্তু দাসীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি।
গাইড বললেন, এটা হলো জনশ্রম্নতি, এতে সত্যের অংশ কতটুকু, আল্লাহ জানেন।
আল্লামা উছমানী সত্যই বলেছেন, ‘তোপকাপে জাদুঘরের প্রতিটি কক্ষে এত অসংখ্য ও বিচিত্র দ্রব্যসামগ্রী রয়েছে যে, দেখে শেষ করা যাবে না একদু’দিনেও; আর প্রতিটি এত আকর্ষণীয় যে, এগুলোর পরিচয় তুলে ধরার জন্য, আলাদা মযমূন দরকার।’
পুরো জাদুঘরে কী পরিমাণ সোনাদানা, হীরা-জহরত ও দুর্লভ সামগ্রী রয়েছে তা আন্দায করাও সম্ভব নয়। একটা কথা বহু যুগ ধরে প্রচলিত রয়েছে যে, তুর্কী সরকার কখনো যদি দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলে তোপকাপে-এ সংরক্ষিত সম্পদ দ্বারাই কিছু দিন সরকারের পুরো ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব।
আল্লামা তাক্বী উছমানী লিখেছেন, ‘প্রথমে এ বক্তব্যটি যখন হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী রাহ.-এর সফরনামায় পড়ি, মনে হলো, যারা এটা বলেছে, হয়ত প্রয়োজনের চেয়ে বেশী অতিশয়তার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তোপকাপে-এর শুধু এই অংশটি দেখে, যেখানে শাহী তোহফা ও উপঢৌকন-সামগ্রী সংরক্ষণ করা হয়েছে, বাস্তবেই নিজের ধারণার ভ্রান্তি পরিষ্কার হয়ে গেলো এবং বোঝা গেলো, কথাটা বহুলাংশেই সত্য। সম্ভবত স্বর্ণরৌপ্য, হীরাজহরত, মণিমুক্তা ও বিভিন্ন দুর্লভ দ্রব্যের এত বিপুল, এত মূল্যবান সঞ্চয় পৃথিবীর অন্য কোন জাদুঘরে নেই।’
আমি বলি, দেউলিয়া হোক তুরস্কের শত্রুরা। এখন তুরস্ক আর ইউরোপের রুগ্ণপুরুষ নয়। রজব তৈয়ব এরদোগানের প্রজ্ঞাপূর্ণ ও গতিশীল নেতৃত্বে তুরস্ক এখন পৃথিবীর শীর্ষ অর্থনীতির দেশগুলোর স্তরে উন্নীত হয়েছে। কামনা করি, তুরস্কের উন্নতি অগ্রগতি যেন অব্যাহত থাকে, সেই সঙ্গে যেন অব্যাহত থাকে তুর্কিস্তানের পথে তার অভিযাত্রা।
***
তোপকাপে জাদুঘর ঘুরে ফিরে দেখার পর আল্লামা উছমানী মু. যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্য করেছেন তা এখানে তুলে ধরা খুবই জরুরি মনে হয়। তিনি লিখেছেন-
‘এ জাদুঘর, কোন সন্দেহ নেই, ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের জন্য অতি চিত্তাকর্ষক এক ‘তামাশাস্থল’, কিন্তু এর চেয়ে বড় কথা এই যে, এটা এক বিরাট শিক্ষাগ্রহণেরও কেন্দ্র। যে সম্পদ, শানশওকত ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষ মানুষের গলা কেটে এসেছে; যেগুলো অর্জন করা এবং রক্ষা করার জন্য মানুষ নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করেছে, এত লড়াই ও যুদ্ধবিগ্রহ করেছে, তার কিছুই তো মানুষ নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। দুনিয়া থেকে যখন সে বিদায় নিয়েছে তখন, যেমন খালি হাতে এসেছে তেমনি খালি হাতেই গিয়েছে। দুনিয়ার এই সব ‘চমকদমক’ অন্যের হাতে গিয়ে পড়েছে, আর শেষ পর্যন্ত তা দর্শক, পরিদর্শক ও পর্যটকদের মনোরঞ্জনের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এটা সেই চিরন্তন সত্য যা মানুষ সবসময় ভুলে যায় এবং ভুলে থাকতে চায়। জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণের সময় মানুষ যদি এই সত্যটি মনে রাখে তাহলে দুনিয়া, যা এখন খুনখারাবি ও অত্যাচার অনাচারের জাহান্নাম হয়ে আছে সহজেই তা হতে পারে সুখশান্তি এবং স্বস্তি ও সম্প্রীতির গুলবাগিচা।’
ঠিক এই অনুভূতি বুকে ধারণ করেই বিষণ্ণ মনে আমরা তোপকাপে জাদুঘরের পরিদর্শন অসমাপ্ত রেখেই বের হয়ে এলাম।
মাগরিবের সময় হতে তখন খুব বেশী বাকি নেই। বাগান ও ফুলবাগিচার মধ্য দিয়ে আবার দীর্ঘ পথ হেঁটে আমরা নিজ নিজ বাসে উঠলাম। আবহাওয়া তখন সত্যি খুব মনোরম ছিলো। বাতাসে শীতের কিছুটা আমেজ ছিলো, কিন্তু তা কষ্টের কারণ তো ছিলোই না, বরং দেহ-মনে যথেষ্ট সতেজতা এনে দিচ্ছিলো।
সুপ্রশস্ত সড়কে গাড়ী দ্রুত গতিতে চলছিলো। মেহমানদের অনেকেই জাদুঘর সম্পর্কে কথা বলছিলেন, সবারই অনুভূতি কমবেশী তাই ছিলো যা আল্লামা উছমানী মু. লিখেছেন।
***
আমার ধারণা ছিলো, বাস এখন হোটেলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে দেখা গেলো বাস এসে থেমেছে বিশাল এক মসজিদের সামনে। সুলতান সোলায়মানের মসজিদ। ১৫৪৯ সালে এর নির্মাণকাজ শুরু হয়, সুলতান ভিয়েনা অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে আসার পর। যেমন বিরাট তেমনি ভাবগম্ভীর, আর তেমনি সুন্দর। জাকজমকপূর্ণ সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ করে, অভিভূত করে, আর অনাড়ম্বর সৌন্দর্য করে আপস্নুত এবং আত্মসমাহিত। সুলতান সোলায়মানের এ বিরাট মসজিদ তার অনাড়ম্বর সৌন্দর্যে আমাদের তেমনি আত্মসমাহিত করলো।
আয়তনের দিক থেকে এটি ইস্তাম্বুলের সবচে’ বড় মসজিদ, আর স্থাপত্যশিল্পের বিচারে পৃথিবীর হাতে গোনা কয়েকটি মসজিদের একটি। মসজিদের মূল ছালাতকক্ষটি দৈর্ঘ্যে ৬৯ মিটার এবং প্রস্থে ৬৩ মিটার। সে যুগে যে ধরনের মোমবাতি বা শামা ব্যবহার করা হতো তার কিছু নমুনা এখনো আট-দশ ফুট উচ্চতায় প্রাচীন শামাদানে স্থাপন করে রাখা হয়েছে। প্রজ্বলিত বাতির ধোঁয়া যেন ভিতরের পরিবেশ নষ্ট না করে সেজন্য প্রতিটি শামাদানের ঠিক উপরে ধোঁয়া বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে অত্যন্ত সুদৃশ্য চিমনির মাধ্যমে। গাইড বললেন, এই ধোঁয়া যেন বেকার না যায় সে জন্য চিমনি থেকে নিয়মিত ঝুল সংগ্রহ করে তা দ্বারা কালি বানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। প্রশংসাই করতে হয়, একদিকে সম্পদের অঢেল ব্যবহার, যা অপচয়ের প্রান্ত ছুঁয়ে যায়, অন্যদিকে চিমনির ঝুলকেও কাজে লাগানোর চিমত্মা, যা দরবেশের ‘কৃচ্ছতা’কেও হার মানায়!
মেহরাবের কারুকাজ সত্যি দেখার মত। সবকিছু যেন জীবন্ত। শিল্পী যেন সবকিছুতে তার প্রাণের ছোঁয়া রেখে দিয়েছেন। এত যুগ পরেও মনে হয়, সবকিছু গতকাল করা হয়েছে।
মেহরাবের সঙ্গে বড় আয়তনের মিম্বর এমনই সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, মনে হয় তা মেহরাবেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সে যুগে লাউডস্পীকার ছিলো না, কিন্তু কক্ষের আয়তন, ছাদের উচ্চতা, খুঁটিগুলোর দূরত্ব এবং গম্বুজ সবকিছুতে এমন প্রকৌশল ব্যবহার করা হয়েছে যেন ইমাম ও খতীবের প্রতিটি কথা পুরো ছালাতকক্ষে সমান মাত্রায় শোনা যায়।
প্রতিটি জানালায় এমন সুন্দর ফুলবোটার কাজ যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। জানালাগুলোর সজ্জায়নে নিযুক্ত করা হয়েছিলো সে যুগের বিখ্যাত শিল্পী তারীফকে। তিনি মদের দোকানেই পড়ে থাকতেন। কিন্তু এ কাজে তিনি এমনই মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন যে, আর মদ স্পর্শ করেননি। কাজ শেষ হওয়ার পর অল্প ক’দিনই তিনি বেঁচে ছিলেন। মসজিদের চার-দেয়ালে উপরের দিকে দৃষ্টিনন্দন তোগরায় কোরআনের আয়াত লেখা হয়েছে, যা মসজিদের ভাবগম্ভীরতা অসম্ভব বাড়িয়ে দিয়েছে। যারাই দেখলেন মুগ্ধ অভিভূত কণ্ঠে বললেন, সুবহানাল্লাহ! গাইড জানালেন, এগুলো উস্তাদ রফীকের লেখা। অত্যন্ত দরদ ও যত্ন দিয়ে এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে তিনি লিখেছেন। একসময় তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। তখন তাঁর নির্দেশনায় তাঁরই এক শিষ্য অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করেন।
মসজিদের স্থপতি হলেন উস্তাদ যীনান, যিনি ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ স্থপতি। এখনো তাঁকে মনে করা হয়, স্থাপত্যবিদ্যার পথিকৃত। সারা জীবনে তিনি একশ ছত্রিশটি মসজিদ, তিনটি হাসপাতাল, চৌদ্দটি বড় সেতু, পঁয়ত্রিশটি প্রাসাদসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নকশা তৈরী করেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, উস্তাদ যীনানের মৃত্যুর পর সমগ্র তুরস্কে তিনশ ষাটটি স্থাপত্যকীর্তি তাঁর স্মৃতিচিহ্নরূপে বহু যুগ ধরে বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো এই জামে সুলায়মানিয়া যা কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে এখনো সগৌরবে বিদ্যমান রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ বহু যুগ বিদ্যমান থাকবে। বার্নাড লুইস লিখেছেন, ‘জামে সোলায়মানিয়া হলো যীনানের সুন্দরতম স্থাপত্যকীর্তি এবং সকল ঐতিহাসিক একমত যে, তিনিই হলেন সর্বকালের সেরা স্থপতি।
উস্তাদ যীনান অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। কথিত আছে, কখনো তাঁর তাহাজ্জুদ কাযা হয়নি।
মসজিদের দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় মেঝেতে একটি লাল মার্বেল পাথরের দিকে ইঙ্গিত করে গাইড বলেছিলেন, এই পাথরটি লক্ষ্য করুন, এর রয়েছে এক চমকপ্রদ কাহিনী। পরে সুযোগ মত আপনাদের শোনাবো। কিন্তু পরে আর সুযোগ হয়নি। তবে আল্লামা তাক্বী উছমানীর সফরনামা পড়ে এর ইতিহাস জানতে পেরেছি যা সত্যি চমকপ্রদ, যা একই সঙ্গে খৃস্টানদের শঠতা এবং উস্তাদ যীনানের অন্তর্দৃষ্টির সুস্পষ্ট প্রমাণ।
সুলতান সুলায়মান তাঁর অছিয়ত মোতাবেক তাঁরই প্রিয় মসজিদের লাগোয়া কবরস্তানে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। আর তাঁর কবরের অদূরেই রয়েছে মহান স্থপতি উস্তাদ যীনানের কবর।
ইতিহাস থেকে জানা যায়, সুলতান সোলায়মান উস্তাদ যীনানকে এমনই মর্যাদা দান করেছিলেন যে, মসজিদের উদ্বোধন তিনি নিজে না করে উস্তাদ যীনানের হাতে চাবি তুলে দিয়েছিলেন। আর সুলতানের উপস্থিতিতে উস্তাদ যীনান আপন হাতে মসজিদের তালা খুলেছিলেন।
মাগরিবের আযান হলো। নামায হলো। মেহমানদের বাদ দিয়ে মুছলস্নী তেমন দেখা গেলো না। গাইড বললেন, আছরের সময় মুছল্লীদের সমাগম বেশী হয়। তিনকাতার পূর্ণ হয়। তবে জুমার জামাতে মসজিদ উপচে পড়ে।
বাস আবার রওয়ানা হলো। এবার হোটেলের উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা হোটেলে পৌঁছে গেলাম। গাড়ী থেকে যখন নামছি, হোটেলের লাউডস্পীকারে তখন আযান শুরু হয়েছে, ঠিক যেন মদীনা শরীফের হৃদয় ও আত্মাকে শীতলকারী আযান!
***
এশার নামাযের পর রাতের খাবার, আরো সঠিক শব্দে ‘নৈশভোজ’ সম্পন্ন হলো। দুপুরের মত সেই বিপুল আয়োজন। আমরা খুব সংক্ষিপ্তভাবে রুটি-সালাদ ও ভুনা গোশত নিলাম, আর শেষে এককাপ ধূমায়িত কফি, যা সারা দিনের সব ক্লান্তি যেন দূর করে দিলো।
আহারপর্ব শেষ হওয়ার পর আমরা হোটেলের সামনে সবুজ মাঠে কিছুক্ষণ পায়চারী করলাম। বিভিন্ন দেশের বহু মেহমানও পায়চারী করছিলেন। সময়টা খুবই আনন্দের মধ্যে অতিবাহিত হলো। আবহাওয়াও ছিলো মোলায়েম। সমুদ্র যে খুব কাছে তা হিমেল বায়ুর প্রবাহ থেকেও অনুভব করা যাচ্ছিলো। আকাশও তেমন মেঘাচ্ছন্ন ছিলো না। পূর্ণ চাঁদ তখন আকাশ-যাত্রা শুরু করেছে। পূর্ণিমার আলো ছিলো, কিন্তু আমাদের ঢাকা শহরে যেমন, ইস্তাম্বুলেও তেমন, বিদ্যুতের আলোঝলমলতার কারণে পূর্ণিমার আলো উপভোগ করার সুযোগ ছিলো না। ঢাকায় অবশ্য পূর্ণিমা উপভোগ করার একটা সুযোগ পাওয়া যায় লোড-শেডিং-এর সুবাদে। কিন্তু এখানে সে সুযোগ নেই। কারণ লোড-শেডিং বলতে এখানে কিছু নেই। দিন-রাতের চবিবশ ঘণ্টা বিদ্যুতের সরবরাহ এখানে নীরবচ্ছিন্ন।
তুমি যে দেশেই থাকো, আকাশের চাঁদের দিকে যখন তাকাও মনে হবে, চাঁদ তোমার একান্ত আপনার। যদিও আমেরিকা এবং কোন কোন বৃহৎ শক্তি চাঁদের দখল নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। হয়ত একসময় চাঁদ চলে যাবে তাদের কারো একক দখলে, কিংবা কয়েকটি দেশের যৌথদখলে। তারপরো চাঁদের সৌন্দর্যে থাকবে সারা পৃথিবীর মানুষের সমান অধিকার। চাঁদের কোন ভৌগলিক সীমারেখা আগেও ছিলো না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। এ চাঁদ আমি যেমন দেখেছি আমাদের দেশের আকাশে, তেমনি দেখেছি হেজাযের আকাশে, আজ দেখছি ইস্তাম্বুলের আকাশে। অতীতে তুর্কিস্তানের মানুষও এ চাঁদ দেখেছে তাদের আকাশে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে মানুষ কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভুলে যায়, তার জীবন-ভূগোলের সীমানায় বন্দী। আমিও ভুলে গেলাম, কোথায় আছি, শুধু মনে হলো আমি পৃথিবীর বাসিন্দা, চাঁদ আমার প্রতিবেশী। এত নিকটের প্রতিবেশী যে, কাছের মানুষকেও অনেক সময় এত কাছের মনে হয় না। চাঁদের আলো যেমন পৃথিবীর সব মানুষ সমান অধিকারে সমানভাবে ভোগ করে, যদি পৃথিবীর সম্পদ তেমনি সমানভাগে ভোগ করতে পারতো, তাহলে পৃথিবীতে অভাব ও দারিদ্র্য বলে কিছু থাকতো না। পৃথিবীটা তাহলে বড় সুন্দর হতো, হয়ত চাঁদের চেয়ে সুন্দর! কোনদিন কি হবে পৃথিবীটা এমন?[3] মনে পড়লো, ১৯৫১-এর ৩০শে আগস্ট থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ইস্তাম্বুল শহরেই একটা আন্তপার্লামেন্টারি সম্মেলন হয়েছিলো। পাকিস্তান থেকে প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁর নেতৃত্বে তিনসদস্যের একটি প্রতিনিধিদল তাতে যোগ দিয়েছিলো। অন্য সদস্যরা হলেন মওলভী তমিযুদ্দীন খাঁ ও খন্দকার আলী আফজাল, তিনজনই ছিলেন বাঙ্গালী। ঐ সম্মেলনে একটি আলোচ্যবিষয় ছিলো পৃথিবীর সম্পদের অসম বণ্টন ও দারিদ্র্য। সেখানে একজন আলোচক অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় বলেছিলেন, চাঁদের আলোর উপর যদি সবার সমান অধিকার থাকে তাহলে পৃথিবীর সম্পদের উপর সবার সমান অধিকার থাকবে না কেন? সম্মেলনে উপস্থিত পৃথিবীর ৩৩টি দেশের প্রায় পাঁচশ প্রতিনিধি নাকি তুমুল করতালির মাধ্যমে তার বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছিলো। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। চাঁদের আলোর মত পৃথিবীর সম্পদের উপর মানবজাতির সমঅধিকার আজও নিশ্চিত হয়নি, হয়ত ভবিষ্যতেও হবে না কোনদিন। হয়ত আরো অনেক সম্মেলন হবে, হবে প্রচুর খানাপিনা, যেমন আমরাও এই হোটেলে সেই খানাপিনার শরীকদার। অভাব ও দারিদ্র্য তখনো ছিলো, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।
চাঁদ-ওঠবে, চাঁদ ডোববে, পূর্ণিমা আসবে, আসবে অমাবশ্যা, অতীতের মত ভবিষ্যতেও মানুষ চাঁদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবে, সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখবে, কিন্তু যুদ্ধ- হানাহানি এবং সবলের উপর দুর্বলের আগ্রাসন, অন্যজাতির সম্পদলুণ্ঠন একইভাবে চলতে থাকবে।
আমাদের এই যে সম্মেলন, এখানেও সুন্দর সুন্দর আলোচনা হবে, প্রবন্ধ পাঠ করা হবে, কিন্তু অন্তত মুসলিম বিশ্বের সম্পদের উপর কি মুসলিম উম্মাহর সমান অধিকার নিশ্চিত হবে? অন্তত মুসলিম উম্মাহর ঐক্য? উত্তর আমারও যেমন জানা আছে তেমনি জানা আছে সবার, অর্থাৎ ‘দিল্লী/ইস্তাম্বুল হনূয দূর অস্ত’।
মানুষের কল্পনা ও চিন্তাশক্তির রহস্য আজো উন্মেচিত হয়নি। শুধু আকাশের ঐ উজ্জ্বল চাঁদটার দিকে তাকিয়ে মনের মধ্যে মুহূর্তে কত বিচিত্র চিন্তার আনাগোনা হয়ে গেলো! চিন্তাশক্তির মত মানুষের কর্মশক্তিও যদি হতো এরূপ সর্বব্যাপী!
আল্লামা তাক্বী উছমানী ১৪০৬ হিজরীর রজব মাসে যখন ইস্তাম্বুল সফর করেছিলেন তখনো ইস্তাম্বুলের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ছিলো। তিনি কি চাঁদ দেখেছিলেন! তাঁর অন্তরেও কি তখন কোন ভাবের উদয় হয়েছিলো! আমার জানতে বড় ইচ্ছে করে, কিন্তু উপায় নেই। এ সম্পর্কে তিনি কিছু লেখেননি। তখন ছিলো প্রচন্ড শীত ও তুষার পাতের সময়। হয়ত তখন আকাশে চাঁদ দেখাই যায়নি।
একখন্ড মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়লো আমারও তন্ময়তা ছিন্ন হলো আমীর ছাহেবের কথায়, ‘চলেন কামরায় ফিরে যাই’।
(চলবে ইনশাআল্লাহ)
[1] তৃতীয় মুতাওয়াক্কিল উদ্দেশ্য; আল মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব আল আববাসী (৮৭০ হি.-৯৫০ হি.)
[2] যদিও এ কাজটিই নিন্দনীয়। কারণ প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি করা হারাম এবং স্রষ্টার সাথে বেআদবী।
[3] এক হলো সম্পদে বনী আদমের মাঝে স্বাভাবিক পার্থক্য। এটা ক্ষতিকরও নয়, নিষেধও নয়। আরেকটা হলো কৃত্রিম বৈষম্য। সম্পদের হক আদায় না করা এবং একে অন্যের উপর যুলুম করার কারণেই কৃত্রিম বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ইসলামী অর্থনীতির নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পদ বণ্টন-ব্যবস্থাপনাই এই কৃত্রিম বৈষম্য দূর করার একমাত্র পথ। (আবদুল মালেক)