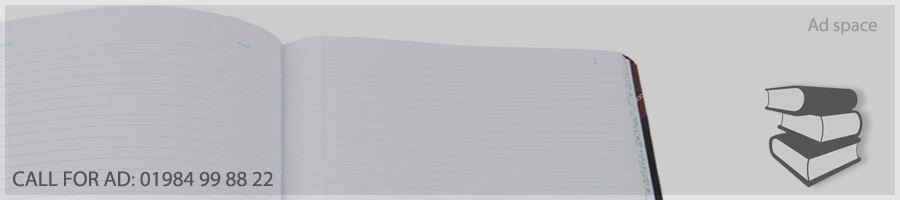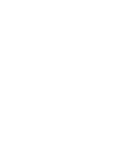১৬ ডিসেম্বর ॥
এত বছরেও অধরা স্বাধীনতা
মার্চ ও ডিসেম্বর মাস এলেই সহকর্মী ও শুভাকাক্সক্ষীদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস নিয়ে কিছু বলা ও লেখার জন্য আবদার শুরু হয়। বরাবরই এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ তৈরি হয় না। কারণ যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ব্যাপক রক্তপাত ও অগণিত আত্মদানের পর বিজয় লাভ করে, কিন্তু বাস্তব জীবনে, নাগরিক জীবনে গণমানুষের স্বাধীনতার স্বাদ অধরাই থেকে গেছে।
অবশ্য ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসটি একটু ব্যতিক্রম। বহু বছর পর সম্ভবত এটাই প্রথম ডিসেম্বর, যখন জনসাধারণের হাত-পা বাঁধা নেই।
একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে নাগরিকরা যেভাবে মত প্রকাশ করতে পারে, কথা বলতে পারে, দাবি-দাওয়া পেশ করতে পারে, বর্তমানে তার আলামত দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও অতিরঞ্জনও হচ্ছে। কারণে-অকারণে দাবি-দাওয়া পেশ হচ্ছে। কিছু হলেই সড়ক আটকে দেওয়ার পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। যদিও শুধুই মতপ্রকাশ বা দাবি-দাওয়া চাওয়ার নামই স্বাধীনতা নয়। কিন্তু এটি একটি আলামত।
এখন আর মিডিয়ার সেল্ফ সেন্সরশিপ নেই। মিডিয়ার ওপর কোনো চাপ নেই। তবে এখনো মিডিয়ার কেউ কেউ ফ্যাসিবাদের পক্ষে বলাবলি করছে, লেখালেখি করছে। কিন্তু একটা গণবিপ্লবের মাধ্যমে গঠিত হওয়া এ সরকার সেখানেও বাধা দিচ্ছে না। বরং সে মিডিয়াগুলোও তাদের দেওয়া শক্তিতেই বা তাদের দেওয়া নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা প্রদানের ভিত্তিতেই টিকে আছে। না-হলে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের মুখোশ নিয়ে যেভাবে একটি গোষ্ঠী বিগত দিনগুলোতে ফ্যাসিবাদকে আগ্রাসী হতে সহযোগিতা করে আসছিল এবং তাদের উচ্ছিষ্ট ভোগ করে আসছিল, এ সরকার সেসবের হিসাব-নিকাশ শুরু করলে অনেকেরই এতদিনে দফারফা হয়ে যেত। অনেক মিডিয়ারই ইতিমধ্যে সমাপ্তি ঘটে যেত।
সারকথা হচ্ছে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে ব্যতিক্রম। সে কারণেই এবার আলকাউসারের মাসিক পরিকল্পনা মজলিসে আমাকে ‘স্বাধীনতা’ ও ‘বিজয়’ সম্পর্কে কিছু লেখার ফরমায়েশ করা হয়, তখনই দু-চারটি কথা বলার ইচ্ছা হয়।
আগেই বলেছি, এবারের ডিসেম্বর বা ৫ আগস্ট পরবর্তী বাংলাদেশের দিকে তাকালে দেখব, সমাজের সকল স্তরের মানুষ দেখতে পাচ্ছেন, এখন কাউকে মত প্রকাশ করতে, নিজের কথা বলতে, সরকারের বিরুদ্ধে বলতে, রাষ্ট্রযন্ত্রের কোনো অংশের বিরুদ্ধে বলতে ভাবতে হয় না। বলার আগে চিন্তা করতে হয় না, বললে আবার আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় কি না! নাকি আবার জেল-জুলুমের শিকার হতে হয়! গুম হয়ে আয়নাঘরে চলে যেতে হয়! তবে সবার সব মতপ্রকাশ ও দাবি-দাওয়া পেশ শুদ্ধ হচ্ছে কি না সেটা ভিন্ন কথা। এটা নিয়ে অনেকের ভিন্ন মতও আছে।
যদিও কায়েমী স্বার্থবাদীদের সৃষ্ট সব ধরনের বৈষম্য এখনো বিরাজমান। সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য তো থেকেই গেছে; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগের মতোই আছে। সেইসাথে সমাজে স্বার্থবাদীদের তৈরি করা শ্রেণিবৈষম্য —উচ্চশ্রেণি, মধ্যমশ্রেণি, নিম্নশ্রেণি– স্বাভাবিক নিয়মে এখনো বহাল।
জালেম ও ফ্যাসিবাদী সরকারের দোসররা এখনো তথাকথিত সাংবাদিকতায় আছে। ক’দিন আগে দেখলাম, তাদের কেউ কেউ দুষ্ট লোকদের সাংবাদিকতার কার্ড বাতিলের প্রতিবাদও করেছে। অথচ যেসব সাংবাদিকের কার্ড বাতিল হয়েছে, তারা আদৌ কি সাংবাদিক ছিল? তারা তো ফ্যাসিবাদের দোসর হিসেবে কাজ করেছে। ফ্যাসিবাদীরা এদেশে জুলুম, নির্যাতন ও একনায়কতন্ত্র চালানোর ব্যাপারে যতটুকু দায়ী, এ দায়ের উল্লেখযোগ্য অংশ এ নামধারী সাংবাদিকদের ঘাড়েও বর্তায়।
এসকল লোকজন তো এখনো বহাল আছে। তাদের মতো লোকেরা, তাদের পত্রিকাগুলো, তাদের টিভি-চ্যানেলগুলোও এখনো আগের মতোই চলছে। কেউ পুরো বোল পাল্টে ফেলছে, কেউ আংশিক, আবার কেউ সুযোগ পেলেই খোঁচাখুচি করছে। বর্তমান সরকার তাদেরও কিছু বলেনি।
স্বাধীনতার ছাপ পড়েছে ইমাম-খতীবগণের মধ্যেও। আমরা দেখব, দেশের খতীব-ইমামগণ বহু বছর পর ইসলামের কথা স্বাধীনভাবে বলতে পারছেন। এখন তাদের বয়ান করার আগে চিন্তা করতে হয় না, এটা বললে না জানি কে চেঁচিয়ে উঠবে অথবা কে জানি আবার কথার মাঝখানেই বেয়াদবি শুরু করবে! নাকি বয়ান শেষে বরখাস্ত পত্র ধরিয়ে দেওয়া হবে! কিংবা দেখা গেল, বয়ান শেষ হতেই সাদা পোশাকধারী সরকারি বাহিনী এসে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। এ ধরনের চিন্তা এখন আর ইমাম-খতীবদের করতে হয় না।
দেশের ওয়াজ-মাহফিলগুলো কিছু তো যোগ্য লোকেরাই করেন। অনেক হক্কানী ভালো আলেম আছেন, যারা সুন্দর ওয়াজ করেন। ভালো ভালো কথা বলেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়, ওয়াজ না আওয়াজ হয়েছে। কারো ক্ষেত্রে এই আওয়াজ শব্দই প্রয়োগ হয়। যারা শুধু শব্দ করাকেই ওয়াজ মনে করে। এতে অবশ্য শ্রোতাদেরও কিছু দায় থাকে। কিছু শ্রোতা শুধু শব্দই শুনতে চায়। এখন সবাই স্বাধীনভাবে ওয়াজ করতে পারছেন। এখন আর মাহফিলগুলোতে ওয়ায়েজগণের নাম নিচে দিয়ে শুরুতে বড় করে অমুক-তমুক নেতাকে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি বানাতে হয় না। স্থানীয় ও সমাজের নিকৃষ্টতম লোকগুলো– নেতা, এমপি, মন্ত্রী ও সরকারি দলের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা এতদিন ছিল, তাদের শুধু নাম দিলেই হত না, মাহফিলগুলোতে দীর্ঘক্ষণ তাদের লেকচারও শুনতে হত।
এই ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ বিজয়ের ৫৩ বছর পূর্ণ হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। সে উপলক্ষে দুটি দিবসও রয়েছে। একটি ২৬শে মার্চ। অন্যটি ১৬ ডিসেম্বর। ২৬শে মার্চে মূলত স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাপ্রধান ও রাষ্ট্রপতি ইয়াহইয়া খান কর্তৃক গণমানুষের দাবি-দাওয়াকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর যখন হামলা ও অপারেশন শুরু হয়, পরদিন ২৬ মার্চ ১৯৭১ স্বাধীনতার ঘোষণা আসে। এরপরই শুরু হয় পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে যাওয়ার লড়াই। সেই যুদ্ধ প্রায় ৯ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণের মাধ্যমে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। অভ্যুদয় হয় স্বাধীন বাংলাদেশের। সে হিসেবে ২৬শে মার্চকে বলা হয় স্বাধীনতা দিবস। ১৬ ডিসেম্বর হল বিজয় দিবস। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২৬ মার্চ। সমাপ্তি ঘটেছিল ১৬ ডিসেম্বর।
স্বাধীনতার ৫৩ বছরে
বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ৫৩ বছর হল। কিন্তু আসলে কি বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে? করলে কতটুকু? স্বাধীনতা লাভের পর অর্থাৎ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ পৃথক হয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশ কী কী পেল?
একটু নিকট অতীতে তাকাই। তকালে অনেক দূরেও তাকানো যায়। বাঙালি জাতির ইতিহাস তো অনেক পুরোনো। যদিও বানিয়ে ফেলা হয়েছিল, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি অমুক জাতির জনক! অথচ বাংলাদেশ ও বাঙালিদের ইতিহাস কত পুরোনো! আর জাতির পিতার আবির্ভাব হয় ’৭১ সালে!
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগে, ব্রিটিশরা যখন এদেশের জনগণের ওপর জেঁকে বসে, তখন তো পুরোটাই ভারতবর্ষ। আমাদের এ অঞ্চলও তাদের অধীনে ছিল। ব্রিটিশ বেনিয়াদের থেকে মুক্তির জন্য পুরো ভারতবর্ষের মতো এ অঞ্চলের মানুষেরও অনেক অবদান ছিল। আগ্রাসী শক্তি ব্রিটিশদের বিদায়ের সময় রাজনীতিতে দুটো মতবাদ তৈরি হয়েছিল। কেউ চেয়েছিল, অখণ্ড ভারত আবার কেউ চেয়েছিল, মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমি। দীর্ঘ বাদানুবাদ, রেফারেন্ডম ও আলোচনা-পর্যালোচনার পর দ্বিজাতি তত্ত্ব অর্থাৎ ‘মুসলমানদের জন্য আলাদা বাসভূমি’ ‘ভারত আলাদা ভূমি’ এর ওপরই শেষ ফয়সালা হয়।
এসব ক্ষেত্রে পুরো ভারতবর্ষের অন্যান্য মুসলিম নেতাদের মতো এ অঞ্চলের মুসলিম নেতাদেরও বেশ অবদান ছিল। বাংলাদেশের শেরে বাংলা খ্যাত এ কে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানীসহ আরো বহু নেতা মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির লক্ষ্যে বা পাকিস্তানের জন্য বেশ জোরালো ভূমিকা পালন করেছেন।
স্বাধীনতা সময়ের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম ছাত্রফ্রন্টের পক্ষ হয়ে কাজ করেন। তখন তিনি একেবারে তরুণ।
অবশেষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের নেতারা জনসাধারণকে হতাশ করে। কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ —যাকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতা বলা হত— তিনি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মারা যান। তার মৃত্যুর পর বিভিন্ন নেতার ওয়াদাখেলাপি, সামরিক কর্মকর্তাদের ক্ষমতার লিপ্সা পাকিস্তানকে শুরু থেকেই লক্ষ্যচ্যুত করে।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে কথা ছিল—
‘পাকিস্তান কা মতলব কিয়া
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’
আরো বলা হয়েছিল, পাকিস্তান হবে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের জন্য, আল্লাহর বিধান কায়েমের জন্য। কিন্তু প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে সংবিধানে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা পেলেও কার্যত আর সেটি বাস্তব রূপ দেখেনি।
১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অধিকাংশ সময়ই সে দেশে সামরিক শাসন ছিল। যে উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছিল, কায়েমী স্বার্থবাদী কিছু নেতা সেটা বাস্তবায়িত হতে দেয়নি।
পরিপূর্ণ শরীয়াহ শাসনে, আল্লাহর বিধিবিধান কায়েম করে একটি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে— এ স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যায়। মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বরঞ্চ সাথে বেড়ে যায় বৈষম্য— প্রদেশে প্রদেশে বৈষম্য, গোত্রে গোত্রে বৈষম্য।
সেই পাকিস্তানেরই একটা বৃহত্তর অংশ পূর্ব পাকিস্তান, যা বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশ। এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যেও একই কারণে ধীরে ধীরে কেন্দ্রের সাথে দূরত্ব বাড়তে থাকে। বিভিন্ন কারণে তারা বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রের বিরাগভাজন হয়েছে। সর্বশেষ ১৯৭০ সালে যখন সাধারণ পরিষদ (তখনকার কওমী এসেম্বলি)-এর নির্বাচন হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার হকদার হয়। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে কোনো আসন না পেলেও পূর্ব পাকিস্তানের দুয়েকটি ছাড়া প্রায় সবকটি আসনই তারা পায়। যে কারণে তারা এককভাবে সরকার গঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু তৎকালীন ইয়াহইয়া সরকার আওয়ামী লীগকে এবং তার নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা দিতে অস্বীকার করেন। বিভিন্ন টাল-বাহানা করতে থাকেন।
এদিকে সময় গড়াতে থাকে, এ অঞ্চলের মানুুষের ক্ষোভও বাড়তে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে রাতদিন বিভিন্ন গ্রুপের, বিভিন্ন জনের মিটিং হতে থাকে। পাকিস্তানের বিভিন্ন বিরোধী দলীয় নেতা এসে তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তাকে যেন দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়, সে দাবিও জানান। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেননি ইয়াহইয়া সরকার ও তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তর দল পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো।
এসব কারণে ধীরে ধীরে এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে ক্ষোভ আরো বাড়তে থাকে। তারা বিভিন্নভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবও চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, যেন সংঘাত এড়িয়ে কোনোভাবে তার হাতে ক্ষমতা চলে আসে এবং এর মাধ্যমে তিনি পুরো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান।
স্বাভাবিক পর্যায়ে তখন সেটাই তার চাওয়া ছিল। এজন্য ২৫ মার্চ তাকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি বিষয়টার সুরাহা করার শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বারবার বৈঠক করছিলেন কেন্দ্রের শাসকদের সাথে। কিন্তু পাকিস্তানের সেনাশাসক ইয়াহইয়া খান এবং নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর গোঁয়ারতুমির কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি।
২৫ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানী আর্মি ঢাকায় অপারেশন শুরু করে। তারা বিক্ষোভরত জনগণের ওপর অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষণা হয় বাংলাদেশ স্বাধীনতার। এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ে।
এ যুদ্ধটি ছিল মূলত চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ। আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিবুর রহমান বা এদেশের জনগণ পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যেতে চায়নি। শেখ মুজিবুর রহমানের তো চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তিনি বিশ্বের একটা বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষমতায় যাচ্ছেন তখন! শুধু মুসলিম রাষ্ট্রই নয়; বরং এটি ছিল বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তর দেশ। সে দেশের তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, শাসক হবেন— এটাই তো স্বাভাবিক চাওয়া ছিল। পাকিস্তানীরাই বাঙালিদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। বাঙালিরা অনেকটা বাধ্য হয়ে এ যুদ্ধ শুরু করে।
এরপর শুরু হয় যুদ্ধ। যা বিশাল রক্তপাত তৈরি করে। নিহত হয় অসংখ্য মানুষ। ভারত আগ থেকেই সুযোগ খুঁজছিল, পাকিস্তান তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার বদলা নেবে। সুযোগসন্ধানী ভারতের জন্য এ সময়টা বেশ কাজে দেয়। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। এর আগেও কয়েকবার পাকিস্তানের সাথে তাদের যুদ্ধ হয়েছে। যেমন ১৯৬৫ সালে। কিন্তু এবার তারা এ সুযোগকে মোক্ষম হিসেবে নেয়। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী বা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একাত্ম হয়ে বছরের শেষ দিকে এসে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ডিসেম্বরে পাকিস্তানী বাহিনী পরাস্ত হয়। তারা আত্মসমর্পণ করে।
আমরা যদি স্বাধীনতার পটভূমির দিকে তাকাই, তাহলে দেখব, এ দেশে যুদ্ধ শুরুই হয়েছিল— মানুষের ভোটাধিকার অস্বীকার, শ্রেণি বৈষম্য, শক্তিশালী গোষ্ঠী কর্তৃক দুর্বল গোষ্ঠীর ওপর নিপীড়ন, নির্যাতন ও তাদেরকে অবজ্ঞার প্রতিবাদে।
যারা যুদ্ধ নেমেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য এটাই ছিল, আমাদের ভোটের মূল্য দেওয়া হয়নি, সুতরাং আমাদেরকে পৃথক হতে হবে, নিজেদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের এ দেশে, আমরা ব্রিটিশ থেকে স্বাধীন হয়েছি বটে, তাদের তাড়িয়েছি বটে, কিন্তু আমাদের এখানে শ্রেণিবৈষম্য থেকেই গেছে। এখনো রয়ে গেছে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে পাহাড়সম তফাৎ।
তখন বলা হত, ২২ পরিবারের হাতে দেশের সিংহভাগ সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে আছে, বাকিরা কষ্টের জীবনযাপন করছে। মানুষ এসব অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নেমেছিল।
এরপর একসময় তো সে স্বাধীনতা অর্জিত হল। কাক্সিক্ষত বিজয়ও এল। কিন্তু পরের ইতিহাস! এর পর পেরিয়ে গেছে অর্ধশত বছরেরও বেশি। বাংলার মানুষের ভাগ্য কি বদলেছে?
এর দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা নেতিবাচক জবাব পাব।
ভোটাধিকার থেকে যুদ্ধ, তারপর
প্রথমেই যদি ভোটাধিকারের দিকটা দেখি, যাকে কেন্দ্র করেই মূলত স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত। আমরা দেখব, যে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পাকিস্তানের শাসনভার পেয়েও শাসন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, সেই আওয়ামী লীগ ও তার দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানই স্বাধীনতার পর প্রথম ভোটাধিকার হরণ করেছিলেন। এমনকি আইন করে! ১৯৭৪ সালে তিনি এমন নীতি প্রণয়ন করলেন, যা ‘কালোকানূন’ নামে পরিচিত। তখন সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে শুধু একটি সরকারি দল বাকশাল করেছিলেন তিনি। কোনো বেসরকারি পত্রিকা রাখা হয়নি। সব বন্ধ করে দিয়ে ৪টা পত্রিকাকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে নেওয়া হয়। বেসরকারি টেলিভিশনের তো তখন প্রশ্নই ছিল না। তখন হয়ে গেছিল ‘এক নেতা এক দেশ’।
এরপর ঘটে যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের বিয়োগান্তক ঘটনা। শেখ মুজিবুর রহমান তার পরিবারের সদস্যসহ কিছু জুনিয়র সেনা সদস্যের হাতে নিহত হন। এরপর দেশে সামরিক শাসন আসে। বিভিন্ন সময় নির্বাচন হয়। কিন্তু দেখা গেছে, কয়েকটি নির্বাচনই মাত্র নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হয়েছে। বাকি নির্বাচনগুলো শুধু তামাশাই ছিল।
আমরা এরশাদ আমলে ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালের নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখব, এগুলো সব ছিল পাতানো।
এরপর বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯০ সালে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় বসলেন। ক্ষমতায় বসার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার বানানোর দাবি ওঠে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে। খালেদা জিয়া প্রথমে মানতে চাইলেন না। একসময় তিনি মানলেন। কিন্তু এর জন্য তো সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন ছিল। আর ততদিনে আওয়ামী লীগসহ আন্দোলনরত বিরোধীদলগুলো তাদের আন্দোলনের অংশ হিসেবে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেছিল। যে কারণে সংবিধান সংশোধন করার মতো সদস্য তখন সংসদে বিদ্যমান ছিল না। তখন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বললেন, তাহলে একটা নির্বাচন অন্তত হোক, যার পরে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আনা হবে। এরপর সে সংসদ ভেঙে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন করানো হবে। সে অনুযায়ী তিনি ১৯৯৬ সালে একটি নির্বাচন করালেন। কিন্তু বিরোধী দল তাতে অংশগ্রহণ না করায় সেটি ছিল যাচ্ছেতাই। অনেকটা ভোটারবিহীন একতরফা নির্বাচন। এরপর এই সংসদই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ করল এবং পরবর্তীতে একই বছর পুনরায় নির্বাচন হল। সে নির্বাচনে শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে।
২০০১ সালে আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন হয়। তখন বিএনপিসহ চার দলীয় জোট ক্ষমতায় আসে।
২০০৮ সালে আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন হয়। তবে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটু ভিন্নরকম ছিল। তারা জোর করে দু-বছর ক্ষমতায় থাকে। তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন কথা আছে। তাদের ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য আছে। তখনকার নির্বাচন কমিশন চালাকি করে কী কী করেছিল, এমন অনেক কথাই চালু আছে। তবুও ২০০৮-এর নির্বাচন-পরবর্তী নির্বাচনগুলোর তুলনায় বা ৮৬ ও ৮৮ সালের নির্বাচনের তুলনায় ভালো ছিল, এ কথা বলতে হবে।
এরপর ২০০৮-এ যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসল, তখন থেকে এ পর্যন্ত নির্বাচনগুলোর কথা তো বর্তমান প্রজন্মও জানে। ২০১৪-এর অটোপাশ নির্বাচন, ২০১৮-এর রাতের নির্বাচন, ২০২৪-এর ডামি নির্বাচন— এগুলো তো এ প্রজন্মের লোকদেরও দেখা।
তাহলে আমরা দেখলাম, যে ইস্যুটাই ছিল ১৯৭১-এর প্রথম বিষয়, স্বাধীনতার পর সে বিষয়েই জনগণ বারবার প্রতারিত হয়েছে। যাদের নেতৃত্বে জনগণ যুদ্ধে নেমেছিল, তারা ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে, নাকি হরণ করেছে?
বাক-স্বাধীনতা
এ তো গেল একটা দিক। মানুষের ভোটাধিকার। আমরা যদি অন্যান্য দিকও দেখি, যেমন বাক-স্বাধীনতার কথা ধরলে দেখব, আরো কত কালোকানূন! যা বিভিন্ন ফ্যাসিবাদী সরকার এদেশের মানুষের ওপর চাপিয়েছে। মানুষের ওপর শত-সহস্র নির্যাতন করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন সরকারের স্বার্থবিরোধী কিছু করলে, বললে বা উদ্যাপন করলেই তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে লেগেছে! বইপত্রে লেখালেখি, পেপার-পত্রিকা, টেলিভিশন, মসজিদ, ওয়াজ-মাহফিল কোনোটাই তাদের ছোবল থেকে মুক্তি পায়নি। কেউ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেনি।
মানুষ দেখেছে যে, বাক স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ৭১-এর যুদ্ধের আগে যা ছিল, পরে তার চেয়েও অনেক কমে গেছে।
জুলুম-নির্যাতন
গেল বাকস্বাধীনতার কথা। এবার যদি জুলুম-নির্যাতনের কথা ধরি, তাহলে তো প্রবীণ নেতাদের অনেকে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। বিগত বছরগুলোর হিসাব আমরা বাদই দিলাম, শুধু জুলাই ২০২৪-এর কথাই যদি ধরি, এই অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার যে গণবিপ্লব গেল, এখানে তারা যত লোককে হত্যা করেছে, প্রবীণ লোকেরা, এমনকি অনেক পুরোনো রাজনৈতিক নেতারাও বলেছেন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানেও পাকিস্তানীরা এত মানুষ মারেনি। বাংলাদেশ যুগ বা তার পূর্ববর্তী কোনো যুগ স্মরণাতীতকালে কোনো জালেম ফ্যাসিবাদী শাসক এ অঞ্চলে এত অল্প দিনে এত মানুষকে মেরেছে— এমন কোনো রেকর্ড, এমন কোনো কথা কারো জানা নেই।
তাহলে কী দাঁড়াল! মানুষ তো কষ্ট করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, আত্মাহুতি দিয়েছে। কিন্তু মুক্তি কি পেয়েছে?
না পায়নি। মানুষ জুলুম থেকে রক্ষা পায়নি। তাদের জান-মাল-ইজ্জতের কোনো রক্ষা হয়নি।
অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা
অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির আশা তো পুরোপুরি অধরাই থেকে গেছে।
আঙুল ফুলে কলাগাছ তো অনেকেরই হয়েছে! সেই ২২ পরিবার থেকে ২২শ পরিবার বা ২২ হাজার অথবা লক্ষ পরিবার তৈরি হয়েছে! কিন্তু এখনো এ অঞ্চলের অসংখ্য লোক, কোটি মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে রাতে ঘুমাতে যায়। তাদের অনেকেই দিনে দু-বেলা পেট ভরে খেতে পান না। অন্যদিকে কিছু লোক সম্পদের বাহাদুরি, বৈধ-অবৈধ সম্পদের পাহাড়, যাচ্ছেতাই খরচ, অপচয়ের মহড়া দিচ্ছে।
আর ক্ষমতাবান ও তাদের নিকটতম লোকদের লুটপাটের কথা তো বিভিন্ন পত্রিকাতেই লেখা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের সম্পদ কীভাবে কুক্ষিগত করে নিয়ে চলে গেছে কিছু লোক, কিছু গোষ্ঠী, কিছু পরিবার!
মোটকথা, এ অঞ্চলের মুসলমানদের অর্থনৈতিক মুক্তিও অর্জিত হয়নি, সামাজিক মুক্তিও আসেনি।
শিক্ষাব্যবস্থা
এখানকার ৯০ ভাগের বেশি মানুষ মুসলমান। পাকিস্তানও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামের নামে। সে অঞ্চলেরই একটা অংশ পূর্ব পাকিস্তান। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশ নামে যার অভ্যুদয় ঘটে। স্বাভাবিক কারণে মানুষেরও সেই পুরোনো আকাক্সক্ষা ছিল যে, এখানে ইসলামী শাসন কায়েম হবে, ইসলামী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে বেড়ে ওঠা সন্তান-সন্ততি ও তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিক্ষা-দীক্ষা ও কৃষ্টি-কালচারে ইসলামী বিষয়াদি পাবে।
কিন্তু সেগুলো অর্জিত হয়নি। কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী, কিছু মতলবী লোকেরা শিক্ষাব্যবস্থাটাকে পুরোপুরি সেক্যুলার বানিয়ে ফেলেছে। সেক্যুলার বললেও কম হয়ে যায়; বরং শিক্ষাব্যবস্থায় তারা ভিনধর্মী ভাব তৈরি করেছে। পৌত্তলিকতা নিয়ে এসেছে। ভিনদেশিদের অপসংস্কৃতি ঢুকিয়ে দিয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা শুধু ইসলামমুক্তই করা হয়নি, বরং তাতে ইসলাম-বিদ্বেষও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাটাই এখনো কর্মমুখী নয়। যা সাধারণ শিক্ষিত লোকেরাও বলে থাকেন। এ কারণেই শিক্ষিত সমাজের লক্ষ লোককে এখনো বেকার জীবনযাপন করতে হয়।
মোটকথা, শিক্ষাতেও কাক্সিক্ষত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। তবুও একটা শিক্ষাব্যবস্থা আছে!
বিচারব্যবস্থা
যদি ন্যায় বিচারের কথা ধরা হয়, তাহলে আমরা দেখব, এখানকার আদালতপাড়া ও বিচার বিভাগ কীভাবে বিভিন্ন সময়ে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে! এ ইতিহাস বিজ্ঞ মহলের অজানা নয়!
কীভাবে বিভিন্ন সরকার আদালতগুলোকে তাবেদার বানিয়ে রেখেছে। মনমতো রায় আদায় করার জন্য প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ চাপ তৈরি করেছে এবং উচ্চ আদালতে দালাল ধরনের দাসত্ব মানসিকতা সম্পন্ন কিছু তথাকথিত বিচারককে নিয়োগ দিয়ে কীভাবে কোর্টপাড়াকে কলুষিত করা হয়েছে এবং মনগড়া রায় আদায় করা হয়েছে। সেসব তো জাতি অনেক দিন থেকেই প্রত্যক্ষ করেছে। আর বিচারের নামে গ্রেপ্তার বাণিজ্য, একশ্রেণির বিচারকদের ঘুষ বাণিজ্য ও ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য যুগ-যুগ পর্যন্ত অপেক্ষার কষ্ট তো সংশ্লিষ্ট মহল ছাড়া অন্য কারো সেভাবে বুঝে আসার কথা নয়।
অতএব ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের আশা শুধু স্বপ্নই থেকে গেছে।
বর্তমানের কাছে আশা
আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক তো হয়ে গেছি। স্বাধীন বাংলাদেশে বসবাসও করছি। কিন্তু স্বাধীনতার সুফল অধরা থেকে গেছে। স্বাধীনতার সেই সুফল আনার এখনই সময়!
এখনকার সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এরা বিপ্লব পরবর্তী সরকার। তারা যে বিভিন্ন সংস্কারে হাত দিয়েছেন, তা যথোপযুক্ত হওয়া দরকার। সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ইসলাম-বিদ্বেষ ও ইসলাম বিরোধীতা মুক্তকরণ!
আমরা তো বলব, ইসলামী শরীয়া কায়েম করুন। কারণ প্রকৃত মুক্তি সে পথেই। জানি, সেটা তারা করবেন না। তাদের যদি এখনই ওই সাহস না থাকে, তাহলে অন্তত ইসলামের মৌলিক জিনিসগুলো তো তারা নিতে পারেন, এর মাধ্যমে কিছু ধাপ তো এগুতে পারেন! সেইসাথে ইসলাম-বিদ্বেষের কোনো কিছুই যেন আর না থাকে, সে ব্যবস্থাটাও তো তারা করতে পারেন।
হরেক প্রকার সংস্কারের ধুম চলছে, বিভিন্ন সংস্কার কমিটি গঠন হয়েছে, সেগুলো যেন যথাযথ হয়; তা যেন গতানুগতিক না হয়। সেগুলো দ্বারা যেন এ অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যগুলো কমে আসে। কেউ যেন ভবিষ্যতে মানুষের অধিকার হরণ করতে না পারে।
মানুষের স্বাধীনতায় —ধর্মীয় স্বাধীনতা, সত্য বলার স্বাধীনতা, হক্বের পক্ষে বলার স্বাধীনতা— কেউ যেন হস্তক্ষেপ করতে না পারে। কেউ যেন কারো চিন্তা কারো ওপর চাপিয়ে দিতে না পারে। ব্যক্তিপূজা, পরিবার-পূজার যে ধারা এদেশে চলছিল, তা যেন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া, পাতানো নির্বাচন— এ বিষয়গুলো যেন পরিপূর্ণ বন্ধ হয়। আইন করে, প্রয়োজনে শাস্তির বিধান করে যেন এগুলো বন্ধ করা হয়— সেই ব্যবস্থা সংস্কারগুলোতে থাকা দরকার। তাহলেই বাংলাদেশের বিজয় হবে। দেরিতে হলেও স্বাধীন বাংলাদেশ সার্থকতা পাবে। না-হয় পৃথিবীর অন্য আট-দশটা রাষ্ট্রের মতো এটাও শুধুই পৃথক একটি রাষ্ট্রই হবে। স্বাধীনতা শুধু নামেই থাকবে। বাস্তবে মানুষ স্বাধীনতার সুফল এতদিন যেমন পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না।